কানেকটম রহস্য
লেখক: সুদীপ চ্যাটার্জী
শিল্পী: সুপ্রিয় দাস
কালো কফিতে চুমুক দিয়ে প্রফেসর খাসনবিশ বললেন, “কসমোলজির আসল মজাটা কি জানো অর্ণব, সব কিছুই এখানে আপেক্ষিক। কোন কিছুই তুমি সাদা কালোতে বিচার করতে পারবে না। কোনটা যে সত্যি আর কোনটা নয় তা ঠিক করার জন্যে যে কনসেপ্টগুলো তৈরী হয়েছে সেগুলো নিয়েও প্রচুর ধোঁয়াশা আছে।”
শনিবারের বিকেল। বৃষ্টি হয়ে শহরের আবহাওয়া একটু হলেও মনোরম হয়েছে। কলেজের পরীক্ষা শেষ। তাই আমি, অলিন, আর সৌরাংশু এসে আড্ডা জমিয়েছি প্রফেসর খাসনবিশের একতলা বাড়িতে। প্রফেসর দেবতোষ খাসনবিশ নামকরা কসমোলজিস্ট, তার ওপর আমাদের অলিনের আপন জেঠু। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় আর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গবেষনা আর শিক্ষকতা করে অবসর নিয়ে ফিরেছেন দেশে। একে তো আমরা এম.এস.সি. অ্যাডভান্স ফিজিক্সের ছাত্র তার ওপর ইদানিং আমাদের ঝোঁক হয়েছে কসমোলজি বা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে। আর এ বিষয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্যে এমন মাই ডিয়ার সায়েন্টিস্ট জেঠু পেয়ে যে আমাদের পোয়া বারো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সুযোগ পেলেই আমরা প্রফেসর খাসনবিশের বাড়িতে গিয়ে হানা দিই।
সৌরাংশু এক খাবলা চানাচুর তুলে বলল, “কিন্তু স্যার, ফিজিক্স এর বেসিক নিয়মগুলো থেকেই তো কসমোলজি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে! তাহলে কি গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে নাকি?” খাসনবিশ জেঠু হেসে বললেন, “একটা মজার ঘটনা বলি শোন। বছর কয়েক আগে জেনেভা কনফারেন্সে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হইচই পড়ে যায়। অপেরা এক্সপেরিমেন্ট বলে একটা গবেষণায় জেনেভা থেকে ইটালি অব্দি হাই–এনার্জি বিম পাঠানো হয়। তাতে দেখা যায় একদল নিউট্রিনো আলোর চেয়েও বেশি গতিবেগে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। সেই দেখে তো সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের আক্কেল গুড়ুম। আলোর চেয়ে বেশি গতি সম্ভব নয়। তাহলে ফিজিক্সের সব নিয়ম ভেস্তে যাবে। আইনস্টাইনের তথ্য হয়ে যাবে ভুল, মহাকাশের যতটা বোঝা গেছে, সব যাবে পাল্টে। সে এক কান্ড।” বলে জেঠু আবার কফিতে চুমুক দিলেন। সৌরাংশু চোখ বড় বড় করে বলল, “তারপর?” তারপর আর কি?” তিনি কাপ নামিয়ে বললেন, “কিছুদিন পরে জানা গেল ভুল মেসারমেন্ট হয়েছিল যান্ত্রিক গোলোযোগের কারনে। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।”
এমনসময় প্রফেসর খাসনবিশ এর মোবাইলটা বেজে উঠলো ঝনঝন করে। নম্বরটা দেখে উনি ইংরেজিতে কারো সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমরা দেখলাম তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।
এক সময় ফোন রেখে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, “আমাকে কালকেই গ্লেন্ফিনান যাওয়ার জন্যে রওনা দিতে হবে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কোনো খারাপ খবর আছে নাকি? আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।” তিনি ভুঁরু কুঁচকে বললেন, “খবর খুবই খারাপ। আমার সহপাঠী ও পুরোনো বন্ধু মার্ক ট্রেভার্স স্কটল্যান্ডের গ্লেন্ফিনানে একটা গবেষণা করছিল। তাকে তিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্কটল্যান্ড পুলিশ থেকে ফোন করে আমাকে জানিয়েছে।” অলিন বলল, “তিনি কি সরকারী গবেষণায় জড়িয়ে ছিলেন? সঙ্গে আরো কেউ ছিল না?” তিনি বসে পড়ে বললেন, “না। সরকারী কাজ নয়। ও একটা নিজস্ব প্রজেক্ট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছিল অনেকদিন ধরে। মাসখানেক আগে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তখন মার্ক বলেছিল যে এই গবেষণা সফল হলে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের দুনিয়ায় সাড়া পড়ে যাবে। এরকম গবেষণায় নানা ধরণের ঝুঁকি থাকে। যাই হোক, চিন্তার যথেষ্ট কারন আছে।”
অলিন বলল, “তুমি একা যাবে কেন? বিপদের সম্ভাবনা আছে যখন আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। দরকার পড়লে তোমাকে সাহায্য করতে পারব।” আমিও সায় দিলাম অলিনের কথায়। প্রফেসর খাসনবিশ হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। তার চোখে গভীর চিন্তার ছায়া।

শেষ পর্যন্ত আমি ও অলিন প্রফেসরের সঙ্গ নিলাম। সৌরাংশু পাসপোর্ট না থাকায় আসতে পারল না। গতকাল এডিনবরায় এসে ট্রেন ধরে আমরা এসে পৌছেছি গ্লেন্ফিনানে। জায়গাটা এতই ছোট যে শহর বলা ভুল হবে, বরং বলা যায় একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সুন্দর করে সাজানো গোটা শয়েক বাড়িঘর। চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। স্কটল্যান্ডে এই এলাকা গুলোকে বলে হাইল্যান্ডস।
স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা পৌঁছে গেছিলাম প্রফেসর মার্কের কাজ করার জায়গাতে। প্রফেসর আগেও নানা কেসে স্কটল্যান্ড পুলিসকে সাহায্য করেছেন বলে সবাই তাকে চেনে। ছোট একতলা বাড়ি। তার স্ত্রী মার্থার সঙ্গে দেখা করে জানা গেল মার্কের আসল কাজের ল্যাব ছিল জঙ্গলের মধ্যে। তার সঙ্গে যারা কাজ করত তাদের মধ্যে অন্যতম আর্জেন্টিনার নিউরোসায়েন্টিস্ট ডক্টর ফিদেল সান মার্টিন। ইনি মার্কের পার্টনার হিসেবে কাজ করতেন। আর ছিল কয়েকজন সহকারী। আমরা গাড়ি করে লক সিয়েলের দিকে চললাম যেখানে মার্ক তার ল্যাব তৈরী করেছিলেন।
ডক্টর মার্টিনের বয়স পঞ্চাশের নীচেই মনে হল। তিনি দেখলাম মার্কের নিরুদ্দেশ হওয়াতে দারুণ ভাবে মুষড়ে পড়েছেন। আমাদের অভিবাদন করে বললেন, “মার্ক যে এরকম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ভাবাই যায় না। আমি তো এই ঘটনার কোনো ব্যাখাই খুঁজে পাচ্ছি না।” প্রফেসর খাসনবিশ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কতদিন ধরে এই গবেষণা করছেন আপনারা একসঙ্গে মিলে, যদি একটু বিশদে বলেন।” ডক্টর মার্টিন আমাদের সামনে একটা চেয়ারে বসে বললেন, “গত অগাস্ট মাস থেকে। প্রায় আট মাস। আমি আর মার্ক দুজনেই এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কাজ করেছি আমেরিকাতে থাকার সময়। আমি তখন ইন্ডিয়ানাতে ব্রেন নিয়ে গবেষণা করছি আর মার্ক করছে কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে। এমন সময় আমরা একসঙ্গে এই বিশেষ গবেষণাটা নিয়ে কাজ করার কথা ভাবি।” প্রফেসর খাসনবিশ জিজ্ঞেস করলেন, “যদি খুব কনফিডেনশিয়াল না হয় তাহলে গবেষণার চরিত্রটা সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যাবে কি? তাতে মার্ক নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে কি ভাবছিল তার একটা সুত্র পাওয়া যেতে পারে।”
ডক্টর মার্টিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “আপনারা নিশ্চয়ই স্রোডিঙ্গারের বেড়ালের কথা জানেন?” আমি আর অলিন মুখ চাওয়াচাওয়ি ওই করলাম। এর মধ্যে আবার বেড়াল এলো কোত্থেকে? স্যার দেখলাম মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।
ডক্টর মার্টিন আবার কথা বলতে যাবেন এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে সশব্দে কাঁচ ভাঙ্গার ঝনঝন শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। ডক্টর মার্টিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিতরের ঘরটা আসলে ল্যাবরাটেরি, এখন যদিও কাজ বন্ধ চলছে। ডক্টর মার্টিন চাবি দিয়ে দরজা খুললেন। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। মাঝারি আকারের ঘরে সার দিয়ে টেবিল। তাতে নানা ধরণের যন্ত্রপাতি রাখা। কাঁচের বিকার, টেস্টটিউব, বুনসেন বার্নারের সঙ্গে রাখা নানা ধরনের জারে রাখা কেমিক্যাল। অন্যদিকে পাতলা একটা পার্টিশন দিয়ে ঘরটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে দেখলাম আধুনিক ধরণের নানা যন্ত্রপাতি বসানো আছে। ফোটন বিম রে গান, জিগার মুলার টিউব, নানা ধরণের ট্রান্সফরমার আর জেনারেটার কিট বসানো ঘরের মধ্যে। একদিকটা কালো পর্দা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে।
কাঁচ ভাঙ্গার শব্দটা কোত্থেকে এসেছিল বুঝতে পারা গেল না। কিছুক্ষণ দেখে ডক্টর মার্টিন বললেন, “মনে হয় পাশের ঘরে জন্তুগুলোর খাঁচায় কিছু ভেঙ্গেছে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “জন্তু মানে আপনারা কি তাদের ওপর কিছু পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন নাকি?” ডক্টর মার্টিন বললেন, “হ্যাঁ। কিন্তু তেমন কিছু নয়। কয়েকটা বাঁদর জাতীয প্রাণী আছে। তাদের মাথায় যন্ত্র পরিয়ে ব্রেন ওয়েব মাপতে হত আমাদের মাঝে মাঝে।” স্যার জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, মার্ক কবে থেকে নিরুদ্দেশ? তার আগে কি কোনো সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছিল?” মার্টিন বললেন, “গত শুক্রবার থেকে। আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল বলে আমরা দুজনেই বেশ খোশমেজাজে ছিলাম। সেদিন রাতে গ্রামে ফিরে তার বাড়িতেই রাত কাটানোর কথা। সন্ধ্যের সময় জিপ গাড়ি নিয়ে বেরোব এমন সময় দেখি আমাদের সহযোগী এডেল এসে বলল স্যারকে খুঁজে পাচ্ছে না। আমি প্রথমে আমল দিইনি। কিন্তু ঘন্টাখানেক হয়ে গেল মার্ক ফিরছে না দেখে আমি তার বাড়িতে ফোন করি। সেখানে সে ফেরেনি। তারপর থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পুলিশে খবর দিই সঙ্গে সঙ্গে। সারা রাত আশেপাশের জঙ্গলে পুলিস তল্লাশি চালিয়েছে কিন্তু কোনো সন্ধান পায়নি।” স্যার বললেন, “আপনাদের ওপরে কি কারো আক্রোশ বা শত্রুতা ছিল। এরকম এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে অনেকেই ফর্মুলা চুরি করার জন্যে পিছনে লাগে।” মার্টিন সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ, সেরকম হয় বলে আমরা প্রথম থেকেই সজাগ ছিলাম। এই রিসার্চ আমরা গ্লাসগো বা এডিনবরায়ও করতে পারতাম কিন্তু গোপনীয়তা অবলম্বন করার জন্যেই গ্লেন্ফিনানে আসা। আমাদের কেউ ভয় দেখায়নি এর মধ্যে। গত আটমাসের মধ্যে সন্দেহজনক তেমন কোনো ঘটনাও ঘটেনি।”
বিকেলের পর যখন আমরা গ্লেন্ফিনানে ফিরে এলাম তখনও অব্দি কোনো সূত্রই পাওয়া যায়নি প্রফেসর মার্কের আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার। আসার আগে যদিও প্রফেসর খাসনবিশ ডক্টর মার্টিনের সঙ্গে একলা অনেকক্ষণ কথা বলেছেন। আমরা ইচ্ছে করেই সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম যাতে মার্টিন সাহেব আমাদের সামনে কথা বলতে অস্বস্তি না বোধ করেন।

সন্ধ্যের সময় প্রফেসর খাসনবিশ একটা নীল রঙের খাম খুলে একতাড়া কাগজ বের করলেন। আমরা আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারছি না। অলিন বলল, “প্রফেসর মার্ক কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন জানতে পারলে?” প্রফেসর খাসনবিশ মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, “মার্টিন আমাকে যা বলল তাই যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে তারা যুগান্তকারী আবিষ্কার করতে চলেছিল, কিন্তু অনেক খটকা আছে রে।” আমরা তো পুরোটাই অন্ধকারে। বললাম, “ব্যাপারটা তো কিছুই বলতে পারছি না। তারপর সকালে স্রোডিঙ্গারের বেড়াল বলে যে ডক্টর মার্টিন থেমে গেলেন সে ব্যাপারটা কি?”
প্রফেসর খাসনবিশ আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, “সেটাই তো আসল ব্যাপার। তোরা ফিজিক্সে ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের কথা পড়িসনি?” অলিন বলল, “হ্যাঁ।পড়েছি বটে। আলোকরশ্মি আসলে দ্বৈত ভাবে ব্যবহার করে। একটা পর্দা যার মধ্যে দু জায়গায় ছিদ্র আছে, যদি তার ওপর আমরা দুটো আলোকরশ্মি ফেলি তাহলে পর্দার অন্যদিকের স্ক্রিনে একটা ইন্টারফেরেন্স প্যাটার্ন তৈরী হয়। কিন্তু যদি এই আলো আমরা কণা হিসবে একে একে ফেলি সেই একই দু ছিদ্রওয়ালা পর্দায় তাতেও দেখা যায় এক্সপেরিমেন্ট শেষ হলে সেই একই প্যাটার্ন পাওয়া যাচ্ছে।”
প্রফেসর বললেন, “তার মানে বুঝলি? ভাব আলোর তরঙ্গ দুটো ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পদ্মফুলের প্যাটার্ন তৈরী করেছে। এবার তুই একটা আলোককণা ফেললি সেটা কোন এক ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পর্দায় এক জায়গায় ফুটকি তৈরী করলো। পরেরটা পর্দার অন্য কোন জায়গায় আরেকটা ফুটকি তৈরী করলো। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর তুই দেখলি সেই ফুটকি ফুটকি বিন্দুগুলো দিয়ে আসলে সেই পদ্মফুলের প্যাটার্ন তৈরী হয়ে গেছে আগেরবারের মত। এবার প্রশ্ন ওঠে এক একটা আলোককণা কি আগেই জানত তার আগের কণাটা কোথায় গিয়ে ফুটকি বানিয়েছে, বা তার পরের আলোককণা কোথায় গিয়ে পড়বে? তা সম্ভব নয়.. তাহলে এই পদ্মফুলের প্যাটার্ন তৈরী হলো কি করে?”
আমরা আবার একে অপরের দিকে দেখলাম। প্রফেসর হেসে বললেন, “এই ছোট্ট এক্সপেরিমেন্টে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির রহ্স্য। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কথা যদি মানতে চাস তাহলে বলতে হয় এই প্রত্যেকটা আলোককণা আসলে নিজেও একটা আলোক তরঙ্গ, আর তাদের চলার সময় আগেকার আর পরের কণাগুলোও চলেছে। সেই জন্যেই তারা একে অপরের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারছে সেই পদ্মফুলের প্যাটার্ন বানাতে। সৃষ্টিতে যত এনার্জি পার্টিকল আছে তারা একসঙ্গে কথা চালিয়ে যায় ভূত আর ভবিষ্যতের এনার্জি পার্টিকলের সঙ্গে। তার মানে একসঙ্গে বর্তমান, ভূত, আর ভবিষ্যত চলছে। যেই সময় একটা আলোককণা চলেছে, সেই সময় তার আগের আর পরের আলোককণাও চলেছে কিন্তু আমাদের চেতনা সেটা আমাদের দেখতে দেয় না। হয়ত একসঙ্গে দশটা পৃথিবী, দশটা মহাকাশ চলেছে আরেক কম্পাঙ্কে, আমি হয়ত এই কথাগুলো তোদের আগেই বলেছি অনেকবার, অথবা পরেও বলব অনেকবার কিন্তু তোদের চেতনায় এই কম্পাঙ্কের এই মুহূর্তটাই ধরা রইলো।” মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। অলিন এর মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলো, “কিন্তু এর মধ্যে বেড়াল এলো কি করে?”
প্রফেসর কফি মেশিন থেকে এক কাপ কফি নিয়ে বললেন, “স্রোডিঙ্গার একটা থিওরিটিকাল এক্সপেরিমেন্টের কথা বলেছেন। একটা বাক্সে একটা বেড়াল আছে, আর তাকে একটি বিষপূর্ণ ফ্লাস্কের সাথে একটি বন্ধ পাত্রে রাখা আছে। আরেকটি বন্ধ পাত্রে আছে রেডিও–অ্যাকটিভ পদার্থ যার একঘন্টার মধ্যে তেজস্ক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা পঞ্চাশ পার্সেন্ট। সেই বাক্সে থাকা যন্ত্র যদি তেজস্ক্রিয়তা শনাক্ত করে, তবে ফ্লাস্কটি ভেঙ্গে যাবে এবং বিষ বেরিয়ে বেড়ালটি মারা পড়বে। এবার তোদের কি মনে হয়, এক ঘন্টা পর বাক্স খুলে কি দেখবি?” আমি বললাম, “যদি তেজস্ক্রিয়তা হয়ে থাকে তাহলে দেখব বেড়ালটা মরে গেছে কিম্বা যদি না হয়ে থাকে দেখব বেড়ালটা বেঁচে আছে!” প্রফেসর মুচকি হেসে বললেন, “কিন্তু কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মতে বাক্স খুলে তুই যাই দেখিস না কেন, বাক্স খোলার আগের মুহূর্ত অব্দি বেড়াল বেঁচেও আছে, আর মরেও গেছে, একইসঙ্গে।” অলিন প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, “ধুত। এমন হয় নাকি?” প্রফেসর তেরছা চোখে তাকিয়ে বললেন, “হবে না কেন? ডুয়াল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে তো বলেইছে ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যত একসঙ্গে চলে। তাহলে যতক্ষণ না কেউ দেখছে একই সময় বেড়াল বেঁচেও আছে, আর মারাও গেছে। এই ধর তোর দাদু মারা গেছে কিন্তু এই মুহুর্তে তিনি বেঁচেও আছেন, কিন্তু তুই কি দেখছিস তোর চেতনাতে সেটাই তোর কাছে আসল। এই যে মানব চেতনা বা হিউমান কনশিয়াসনেস, মার্করা গবেষণা করছিল এটাকেই নিয়ে।”
আমার বা অলিন দুজনেরই কথা বলার অবস্থা ছিল না। প্রফেসর বললেন, “কালকে ওদের ল্যাবের পিছন দিকের জঙ্গলে একটু খোঁজাখুঁজি করতে হবে যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।” আমরা যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেকরাতে একবার উঠে দেখি টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে ল্যাপটপে কাজ করে যাচ্ছেন প্রফেসর খাসনবিশ।

সকালে খবরটা বজ্রপাতের মত শোনালো। ডক্টর মার্টিনের ল্যাবে রাতে কে যেন হামলা করেছিল। মার্টিন সাহেব পাগলের মত হয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে তাকে কোনোরকম ইনজেকশন বা ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল। প্রফেসর মার্কের স্ত্রী মার্থার কাছ থেকে খবরটা পেয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম জঙ্গলের মধ্যে তাদের ল্যাবের কাছে। ততক্ষণে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। মার্থা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি প্রফেসরকে দেখে বললেন, “প্রথমে মার্ক কোথায় হারিয়ে গেল? তারপর মার্টিনের এই দশা। আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।”
প্রফেসর কোনো কথা না বলে ভিতরে ঢুকে সব পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন। যাওয়ার আগে আমাদের চোখ দিয়ে ইশারা করলেন বাড়ির বাইরে ও জঙ্গলের মধ্যে অনুসন্ধান করতে যদি কিছু চোখে পড়ে। সেই মত আমি আর অলিন বাড়ির চারপাশে ঘুরতে শুরু করলাম। বাড়ির পিছন দিকটায় ঘন জঙ্গল শুরু হয়েছে। কোনো রকম কাঁটাতার বা পাঁচিল বলে কিছু দেখতে পেলাম না। আমরা ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।
জঙ্গলটা বাইরে থেকে যতটা সুন্দর মনে হচ্ছিল ভিতরে ঢুকে ততটাই গভীর ও রহস্যময় মনে হতে লাগলো। গাছের পাতা এত ঘন হয়ে আছে যে সূর্যের আলো মাটিতে পড়ছে না বললেই চলে। সকালের শিশির শুকনো পাতা আর ঘাসের ওপর পড়ে নরম হয়ে আছে। আমরা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম পায়ে চলা পথ বলে কিছু নেই। একদিকে জঙ্গল খাড়া হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে আর অন্যদিকে নিচু হয়ে একটা জংলা জায়গায় নেমে গেছে। ফিরে আসব বলে পা ফেলেছি এমন সময় অলিন আমাকে ইশারা করে দাঁড়াতে বলল। সে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। আমাকে চোখের ইশারা করে সে নামতে লাগলো নীচুর দিকে, যেখানে জলাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পিছন পিছন আমিও নামলাম। প্রতি মুহুর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি কেউ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। নীচে পৌছে দেখি জলার একপাশে সারি সারি খাঁচা। খাঁচা গুলো নানা আকারের। কোনটা বড় কোনটা ছোট। কয়েকটা খাঁচা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা আছে। অলিন সামনের দিকের একটা বড় খাঁচার ওপর থেকে ত্রিপল সরাতেই আমরা চমকে উঠলাম। ভিতরে প্রায় দশ হাত লম্বা একটা কুমির। আমরা চোখাচুখি করলাম। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে। আরেকটা খাঁচার ওপর থেকে ত্রিপল সরিয়ে দেখতে পাওয়া গেল একটা বিশাল মনিটর লিজার্ড। এর ওপরেই মনে হয় পরীক্ষা চালাত মার্টিন সাহেবেরা। আরেকটা ত্রিপল সরিয়ে দেখতে পেলাম রক্তমাখা কিছু জামাকাপড়। এখানে যে কিছু ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে তাতে সন্দেহ রইলো না।
এদের ঘন্টাখানেক পর আমরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে এগোলাম। খাঁচাগুলোর মধ্যে আমরা প্রায় প্রায় দশ পনেরো রকমের কুমির আর অন্যান্য সরীসৃপ দেখতে পেয়েছি। রক্তমাখা জামা ছাড়া আর কোন সুত্র পাইনি। প্রফেসরকে জানাতে হবে এই ব্যাপারে।
ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি ডক্টর মার্টিন উদভ্রান্ত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। ল্যাবের প্রায় সব যন্ত্রপাতি আর কাঁচের জিনিসপত্র ভেঙ্গে ছড়িয়ে আছে মাটির ওপর। কয়েকজন ডাক্তার মার্টিন সাহেবকে পরীক্ষা করছেন কিন্তু তাতে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম প্রফেসর একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন একটা ডায়রির। কোনো সুত্র কি পাওয়া গেল?
আমরা গিয়ে তাকে ঘটনার কথা জানাতে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এলেন আমাদের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে। জায়গাটা দেখে তার চোখে একটা ঝিলিক দিয়ে গেল লক্ষ্য করলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসে তিনি পুলিস অফিসারকে গিয়ে বললেন, “এখানে যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করত তাদের সম্পর্কে কি খোঁজ নেওয়া হয়েছে?” পুলিস ইন্সপেক্টার খাতা দেখে বললেন, “ডক্টর মার্টিনের কথা অনুযায়ী এখানে এডেল আর জেফ্রি বলে দুজনে তাদের সঙ্গে কাজ করত। জেফ্রি নাকি তিন সপ্তাহের ছুটি চেয়ে বাড়ি গিয়েছিল ইন্ভার্নেসে। এডেলের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। যেদিন মার্ক নিখোঁজ হয় সেইদিন সে এখানেই ছিল তারপর তাকে ছুটি দেওয়া হয়।” প্রফেসর কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর ঝড়ের মত গিয়ে ঢুকলেন ল্যাবের মধ্যে। ডাক্তারদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আবার এগিয়ে গিয়ে কি সব খুঁজতে লাগলেন ভাঙ্গা জিনিসপত্রের মধ্যে। এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের বললেন, “পুলিস ইন্সপেক্টার কে ডেকে নিয়ে আয়। আজ রাতে আমাদের এখানেই থাকতে হবে।”

সন্ধ্যে সাতটা বাজলো। আমরা বাড়ি ফিরে না গিয়ে এখানেই রয়ে গেছি। দুপুরের পর ডক্টর মার্টিনের অবস্থা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রফেসর যে কেন এখানে রয়ে গেলেন সেটা এখনো আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। তার ওপর আমরা বাড়ির ভিতরে না ঢুকে বসে আছি বাইরে, যেখান থেকে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে সেইখানে। বিকেলের পর থেকেই এখানে এমন শীত পড়তে শুরু করেছে যে বলার নয়। এই গরমকালে এমন ঠান্ডা যে পড়তে পারে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। ভাগ্যিস জ্যাকেট সঙ্গে রেখেছিলাম।
প্রফেসরকে কোনো প্রশ্ন করেই কোনো সুবিধে হয়নি। উত্তর পাওয়া যায়নি। চুপ করে বসে থাকার নির্দেশ পালন করতে করতে যখন অলিন আর আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা গাড়ির আলো দেখতে পাওয়া গেল। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছি। এই কি তবে অপরাধী? গাড়িটা এসে থামল বাড়ির সামনে। দুজন নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। আমরা যতটা সম্ভব আড়াল রেখে তাদের পিছু নিলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঢুকে তারা এগিয়ে গেল আমাদের সকালের দেখা কুমিরের খাঁচাগুলোর দিকে। আমরা প্রায় কুড়ি হাত তফাৎ রেখে অনুসরণ করে যাচ্ছি। খাঁচাগুলোর কাছে এসে একজন একটা খালি খাঁচার কাছে বসে পড়ল। একটা চাবি দিয়ে খাঁচার দরজা খুলে যেই সে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় প্রফেসরের গলা শোনা গেল, “পুট ইওর হ্যান্ডস আপ।” দেখলাম প্রফেসর কখন উঠে গেছেন আমাদের লুকিয়ে রাখা জায়গা থেকে। তক্ষুণি অনেকগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল। আগন্তুক পকেট থেকে একটা বন্দুক বার করতেই প্রফেসরের বন্দুক গর্জে উঠলো। অন্য ব্যক্তি তখন পালাতে শুরু করেছে। আমি আর অলিন দেখলাম কিছু না ভেবেই তার পিছনে দৌড়তে শুরু করেছি। কাছাকাছি পৌছে প্রায় চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে অলিন লোকটার পা জড়িয়ে ধরল। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। এমন সময় শোনা গেল হুইসিল আর হুইসিল ছাপিয়ে প্রফেসরের গলা, “ইন্সপেক্টর, এরেস্ট দেম।”
ততক্ষণে বড় বড় টর্চের আলো পড়ে জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। কয়েকজোড়া ভারী বুটের শব্দ শুনে বুঝলাম পুলিশকে আগে থেকেই বলা ছিল। প্রফেসেরের সামনে যে লোকটা হাত উঁচু করে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং ডক্টর মার্টিন। তার আঙ্গুলে গুলি লেগে রক্ত পড়ছে। আর আমাদের সামনে যে আছে সে মুখ ঢেকে রেখেছে কালো টুপিতে। প্রফেসরের হাতের টর্চের আলো তার মুখে পড়ল। তার তীক্ষ্ন স্বর শোনা গেল, “পুট দি মাস্ক ডাউন।” আগন্তুক রক্তজল করা চোখে তার দিকে তাকিয়ে টুপিটা খুলে ফেলতেই আমাদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। একি? এ যে মার্থা।
পুলিশের টর্চের আলোতে প্রফেসর এগিয়ে গিয়ে সেই খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন যার চাবি খোলা হয়েছিল। তারপর খাঁচার দরজার লিভার ঘোরাতেই মাটিতে একটা গুপ্ত দরজা খুলে গেল ঘরঘর শব্দে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। প্রফেসর বললেন, “ভাববেন না। আলোর ব্যবস্থা আছে। নীচে নেমে সুইচ টিপতেই জায়গাটা বৈদ্যুতিক আলোতে ভরে গেল। লম্বা একখানা প্যাসেজ। খানিকটা এগোতে একটা ঘর। তাতে খাঁচায় করে রাখা আছে অনেকগুলো বাঁদর। আমাদের দেখে তারা খিঁচ খিঁচ করে ডেকে উঠলো। আরও খানিকটা এগিয়ে একটা ঘরে পাওয়া গেল নানা ধরণের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। ওপরের ল্যাবরাটেরি থেকে এই ঘরটা প্রায় তিনগুণ, কয়েকটা কাঁচের বাক্স পড়ে ভেঙ্গে গেছে, সেই ঘরেরই একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়ির ভিতরের ল্যাবরাটেরিতে। আর ঘরের এককোণে একটা বড় খাঁচায় অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে একজন মানুষ। প্রফেসর মার্ক।

আমরা গোল হয়ে বসেছি প্রফেসর মার্কের বাড়িতে। আমি, অলিন, প্রফেসর খাসনবিশ আর প্রফেসর মার্ক ছাড়া আছেন স্থানীয় পুলিস ইন্সপেক্টর। প্রফেসর খাসনবিশ বলতে শুরু করলেন, “প্রথম দিন মার্থাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ডক্টর মার্টিন আর মার্থা এরা বোধহয় দুজনেই জানত না যে আমি মার্ককে অনেক আগে থেকেই চিনি। সে কস্মিনকালেও বিয়ে করেনি। আর আমার সঙ্গে তো তার কথাই হয়েছিল মাসখানেক আগে। কিন্তু তখন মার্ককে খুঁজে বের করা আমার প্রধান চিন্তা। তাই পুলিশকে জানানোর ঝুঁকি নিইনি।
প্রথমে মার্টিন কে দেখে আমি সন্দেহ করিনি কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগে। আমাদের কথা বলার সময়ে কোথায় যেন একটা কাঁচ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু কোথায়? ল্যাবে সব ঠিকঠাক ছিল। মার্টিন বলে পাশে জন্তুদের ঘরে কোনো পাত্র ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু সেই ঘরটা কোথায়? বাড়িটা তো খালি দু কামরার। খুঁজে খুঁজে কিছু দেখতে পাইনি। তখনই আমার সন্দেহ হয় নিশ্চয়ই মাটির তলায় কোনো অন্য ল্যাব তৈরী করেছিল মার্ক। তাকে আমি চিনি তো। এরকম গুপ্ত গবেষণা করতে গেলে যতরকম সাবধানতা অবলম্বন করা যায় সবই সে করবে। তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাও ঠিক করে কিছু বুঝতে পারিনি। মার্টিন বলেছিল তারা হিউমান কনশিয়াসনেস নিয়ে গবেষণা করছিল। বাড়িতে গিয়ে নেট সার্চ করে বুঝতে পারি মার্টিন নিউরোসাইন্টিস্ট ঠিকই, কিন্তু শত্রুদের কাছে সরকারি বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা পাচার করার অভিযোগে তাকে বার্কলে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এটাও জানতে পারি যে মার্থা আসলে বার্কেলের আরেকজন নিউরোসাইন্টিস্ট। তখনই খটকাটা ঠিক বলে জানতে পারি। মার্ক, মার্থা তো তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, তাই না?”
প্রফেসর মার্ক মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ। আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিনি যে তার সঙ্গে চক্রান্ত করে মার্টিন আমার ফর্মুলা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। ওই লোকটা আবার নিজেকে আমার পার্টনার বলে চালাচ্ছিল তোমাদের।” প্রফেসর খাসনবীশ হেসে বললেন, “দ্বিতীয় দিন তোমার লেখা ডায়রিটা হাতে পড়তেই আমার কাছে অনেকটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে আসে।” আমি একটু কিন্তু কিন্তু করে বললাম, “কিন্তু মার্টিন তাহলে ওই ডায়রিটা অবহেলায় সামনে ফেলে রেখেছিল কেন? আর ওরকম পাগল সেজে নাটক করার মানেটাও তো বুঝছি না।” প্রফেসর খাসনবিশ মার্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি একবার পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে বল।”
প্রফেসর মার্ক আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বিজ্ঞানের একটা রহস্য সমাধান করা থেকেই এই গল্পের শুরু। তোমাদের সঙ্গে মজা করলেও মার্টিন আসল কথাটা তোমাকে ভুল বলেনি। পুরো ব্যাপারটাই শুরু হয়েছিল স্রডিঙ্গারের বেড়ালের সমস্যা দিয়ে। একই সময় একটা বেড়াল মৃত এবং জীবিত, কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নিয়ম তাই বলছে। তাহলে মানবচেতনাই কি আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখছে সৃষ্টির রহস্য জানতে? চেতনা অথবা কনশিয়াসনেস সেই সুত্র যা বিশ্বব্রহ্মান্ডকে চালনা করছে। যতক্ষণ না চেতনা আমাদের দেখাচ্ছে কোনো কিছু, আসলে কোন ঘটনাই হচ্ছে না আমাদের জন্যে, তারা একই সঙ্গে হয়ে চলছে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যতে। শুধু আমাদের কাছে নয়, প্রতিটি প্রাণীর কাছে। আমরা জানি না বেড়াল বেঁচে থাকবে কি না বন্ধ বাক্সের ভিতরে? এই প্রশ্ন জন্ম দেয় আরেক প্রশ্নের। আমরাও কি আদৌ বেঁচে আছি? যতক্ষণ না কেউ তার কনশিয়াসনেস দিয়ে আমাকে দেখছে। আবার সেও কি বেঁচে আছে যে আমাকে দেখছে? এ এক আবহমান কাল থেকে চলতে থাকা ফীডব্যাক লুপ। সৃষ্টির সমস্ত রহস্য লুকিয়ে এই প্রশ্নের মধ্যে? তাহলে আমরা এর উত্তর জানব কি করে? যদি কোনরকমে আমরা মানব চেতনা বা হিউমান কনশিয়াসনেস থেকে বেরোতে পারি। এই নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করি প্রায় বছর দশেক আগে। ব্রেনের মধ্যেকার নিউরনদের আচরণ নিয়ে রিসার্চ শুরু হয়। মস্তিষ্কে নিউরনদের ব্যবহার আর পারস্পরিক কার্যকলাপ নিয়ে ম্যাপ তৈরী করা কে বলে কানেকটম। এই কানেকটম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি জানতে পারি মানুষের মস্তিষ্কের চেতনা আসলে তিন ভাবে ভাগ করা যায়। একে বলে কোয়ান্টিফাইং কনশিয়াসনেস। ব্রেনের পিছন দিকটা আসলে রেপটাইল কনশিয়াসনেস। কুমির জাতীয় প্রাণীর মধ্যে এই চেতনা পাওয়া যায়। এই চেতনার প্রধান চিন্তাধারা হল খাওয়ার চিন্তা, শিকার ধরার চিন্তা। মাঝখানটা হল মানকি কনশিয়াসনেস, এই অংশের চেতনা সাহায্য করে সামাজিক ব্যবস্থা বুঝতে পারার। কিন্তু মানুষের সামনের দিকের ব্রেন যেখানে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স আছে সেই চেতনায় মানুষ ভবিষ্যতের চিন্তা করে। ভবিষ্যতে কোনো বিশেষ ঘটনার সম্ভাব্য ফলাফল কি কি হতে পারে এই চিন্তাধারা আছে শুধু মানুষের” প্রফেসর মার্ক একটু দম দেওয়ার জন্যে থামলেন।
তাকে একটু বিশ্রাম নিতে দিয়ে প্রফেসর খাসনবিশ বললেন, “এই জন্যেই মার্ক বেশ কয়েকটা রেপটাইল জাতীয় প্রাণী আর বাঁদর দের ব্রেনওয়েভ পরীক্ষা করছিল। তার রিসার্চের কথা সে লিখে রাখে তার ডায়রিতে, কিন্তু সে যাবতীয় তথ্য লিখত সাঙ্কেতিক ভাষায় তাই কেউ বুঝতে পারত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই সাঙ্কেতিক ভাষাটা আসলে সংস্কৃত। মার্কের সংস্কৃতের ওপর চিরকাল একটা দুর্বলতা আছে। ভাগ্যিস, না হলে আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না। মার্কের উদ্দেশ্য ছিল হিউমান কনশিয়াসনেস অর্থাৎ মানবচেতনা থেকে বেরিয়ে এসে সৃষ্টিকে দেখতে পাওয়ার একটা উপায় বের করার। তার কথায় জানতে পেরেছি ব্রেনের মধ্যে একটা অংশ যাকে ক্লসট্রম বলা হয় সেই হল মানবচেতনার প্রধান কারণ। এখন মার্ক এমন একটা আবিষ্কার করেছিল যাতে এই ক্লসট্রম কে কিছুক্ষণের জন্যে অচল করে দেওয়া যায়। সেই ইনজেকশন নিলে মানুষের কোনো চেতনা থাকবে না, ঠিক কি না, মার্ক?”
মার্ক বললেন, “ঠিক। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধে হচ্ছিল। এই ক্লসট্রম আসলে প্রতিটা জানোয়ারের মধ্যেই থাকে কিন্তু চেতনার সমতা সমান হয় না। এখন যদি আমি চেতনার পরিধির বাইরে চলে যাই তাহলে হিউমান কনশিয়াসনেস ছেড়ে বেরোলেও আমি কিছুই দেখতে পারব না, কিছুই বুঝতে পারব না কোয়ান্টাম ফিজিক্সের রহস্য। উদ্ভ্রান্তের মত বসে থাকব খোলা চোখে। কিন্তু সেটা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই আমি পরীক্ষা চালাতে লাগলাম ব্রেনের একেকটা অংশ অচল করা যায় কি না। ভাবো যদি আমি মানকি ব্রেন আর প্রিফ্রন্টাল করটেক্স অচল করে দিই, তাহলে রেপটাইল ব্রেন সচল থাকবে। তাতে কি কোন তফাৎ হবে? মানুষ কি গতানুগতিকতার বাইরে কিছু দেখতে পাবে? হিউমান কনশিয়াসনেস আর রেপটাইল কনশিয়াসনেস এ কি সৃষ্টির নিয়ম অন্যভাবে দৃষ্টিগোচর হয়? এখনো জানা নেই। একমাত্র উপায় যখন একজন মানবচেতনার বাইরে যাবে অন্য কেউ তাকে চালিত করবে যন্ত্রের সাহায্যে যাতে তার দেখতে পাওয়া ঘটনার ব্রেনম্যাপিং সম্ভব হয়। হয়ত এই মুহুর্তে আমরা চোখে অদ্ভুত কিছু দেখতে পাব না, কিন্তু কসমোলজির অনেক রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে এতে। কিন্তু কাজ শুরু হওয়ার আগেই মার্টিন এসে আমাকে বন্দী করে ফেলল। যদিও আমার কাছ থেকে সে কোন কিছুর ফর্মুলাই আদায় করতে পারেনি।”
অলিন জিজ্ঞেস করলো, “কিন্তু ব্যাপারটা সে করলো কিভাবে?”
প্রফেসর খাসনবিশ উত্তর দিলেন, “মার্থার সঙ্গে মার্টিনের যোগাযোগ ছিল। তারা জানত ওই ইনজেকশন আর তার ফর্মুলা বিক্রি করতে পারলেই তাদের হাতে বিরাট পরিমাণ টাকা আসবে। মার্টিন চলে আসে গ্লেন্ফিনানে। ল্যাবে গিয়ে প্রথমেই সে জেফ্রিকে আর মার্ককে কব্জা করে। সেটা কোন ব্যাপারই নয়। মার্থা কে দেখে তোমরা কেউই সন্দেহ করবে না। পিছন থেকে একটা ইনজেকশন ফুটিয়ে দিলেই হলো। মার্থার কাছ থেকে জেনে ল্যাবে থাকা ওষুধপত্র আর ইনজেকশন নিতেও তাদের অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এমন সময় জেফ্রি জ্ঞান পেয়ে তাদের আক্রমণ করে। এমন সময় কি আর তাকে না সরিয়ে দিলে কাজ হাসিল হয়। জেফ্রিকে খুন করে দুজনে ফাঁপরে পড়ে। ফর্মুলা না পাওয়া অব্দি মার্ককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আবার জেফ্রির মৃতদেহ পাচার করাও দরকার। শেষ পর্যন্ত তার দেহকে কেটে টুকরো করে তারা কুমিরের খাঁচায় ফেলে দেয়। যাতে কোন ভাবেই কেউ তার মৃত্যুর কথা জানতে না পারে। বেচারা জেফরি।
এরপর সন্ধান শুরু হয় ফর্মুলার, কিন্তু কোথায় খুঁজবে? এদিকে হাতে সময় নেই। এমন সময় তারা চমত্কার উপায় ভাবে। মার্ককে মাটির তলায় বেহুঁশ করে রেখে মার্থা পুলিশের কাছে খবর দেয় নিজেকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে। তাতে একটা সুবিধে, মার্থা মার্কের বাড়িতেও থেকে খুঁজতে পারবে যদি সেখানে থাকে ফর্মুলা। এডিলও আসলে তাদের হয়েই কাজ করত। তাই সে মার্টিনের কথায় সায় দিয়ে জবানবন্দী দিয়েছিল পুলিশের কাছে। এদিকে মার্টিন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আমি এসে পড়ে তাদের কাজে ব্যাঘাত হচ্ছিল। যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা যায়। তাই কি কাল অবশেষে মার্টিন তোমাকে জানিয়েছিল আমার কথা?”
মার্ক হেসে বলল, “হ্যাঁ। সে আমাকে হুমকি দেয় ফর্মুলা না দিলে তোমাকে আর আমাকে দুজনকেই খুন করবে। আমি তাকে বলি সেই ইনজেকশন নিলে সে নিজেই জেনে যাবে ফর্মুলা। আমাকে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না তার। সে ইনজেকশন নিয়ে নেয়, তার চেতনা লোপ পায়। উদ্ভ্রান্তের মত বসে থাকে সে। প্রায় চোদ্দ ঘন্টা এই ওষুধের প্রভাব থাকে। আমি ভেবেছিলাম এই সুযোগে ডায়রিটা নিয়ে পালাব, কিন্তু এডিল আর মার্থা যে একসঙ্গে সেখানে থাকবে আমার জানা ছিল না। তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়, জিনিসপত্র ভেঙ্গে পড়ে, আমি কোনরকমে তাদের চোখ বাঁচিয়ে ডায়রিটা ফেলে দিই তোমার উদ্দ্যেশে, যদি তোমার নজরে আসে। শেষপর্যন্ত আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে তারা। তারপরের ঘটনাটা তো তোমার জানা।”
প্রফেসর খাসনবিশ বললেন, “সকালে খাঁচাগুলো দেখেই আমি গোপন রাস্তার কথাটা বুঝতে পারি। ল্যাবের ভিতরে কুমির রাখা বিপজ্জনক তাই ভূমিগত ভাবে একটা রাস্তা ল্যাবের তলা দিয়ে এদিকে এসেছে তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। রক্তমাখা জামাকাপড় গুলো পেয়েই বেচারা জেফ্রির পরিণতি বুঝতে অসুবিধে হয়নি, তখনই পুলিশকে বলে এডিলকে পাকড়াও করতে বলি। পুলিশের দু ঘা খেয়েই সে সব স্বীকার করেছে। আমি জানতাম আজ ওরা তোমাকে নিয়ে পালাতে চাইবে। অন্য কোথাও ঘাঁটি করা দরকার। ফর্মুলা না পেলে কোনো লাভ হবে না তাদের, বরং তোমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিলে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পুলিশের নজরদারি কড়া হয়ে গেছে। আর দেরী করলে চলবে না। বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া চলবে না, তাই পিছনের গুপ্ত পথ নিয়েছিল। যাক, অবশেষে তোমাকে সুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেছে। তোমার ফর্মুলাও অক্ষত আছে। আর কোনো চিন্তা নেই। তুমি আবার কাজ চালিয়ে যাও। যদি মহাসৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে পারো!”
মার্ক কৃতজ্ঞ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, “হয়ত আমরা এই সময়তে দাঁড়িয়েই জেনে গেছি মহাসৃষ্টির রহস্য, কে বলতে পারে? যতক্ষণ না কেউ বেড়ালের বাক্স খুলছে কোনো সম্ভাবনাই কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?”
Tags: কানেকটম রহস্য, দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী, সুদীপ চ্যাটার্জী, সুপ্রিয় দাস
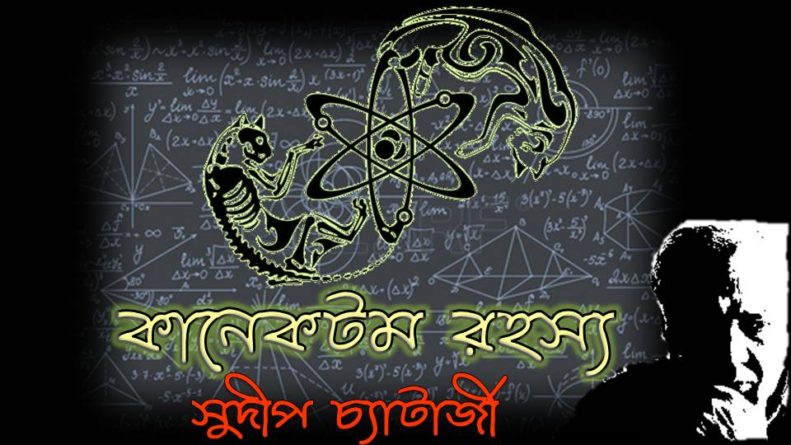

শিশুতোষ গল্প, স্কটল্যান্ডের পুলিশ বিদেশের একজনকে ফোন করলো এটা জানাতে যে তার বন্ধু নিখোঁজ যখন তার ‘বৌ’ রয়েছে ওখানে??
আপনি সঠিক বলেছেন।কিন্তু প্রফেসর আগে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি তে নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলে পুলিশ মহলে তাকে অনেকে চিনতো।বৈজ্ঞানিক মহলে কেউ নিখোঁজ হলে যদি তার কলিগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়,অনেক সময়েই বাড়ির লোকেরা কাজের ব্যাপারে কিছু বলতে পারে না।তবে আপনার কথা মাথায় রাখবো।অনেক ত্রুটি আছে প্রথম চেষ্টায়।পরের বার ঠিক করার চেষ্টা করবো।পরে দেখার জন্যে ধন্যবাদ 🙂
দারুণ লাগল গল্পটা। কল্পবিজ্ঞানের রহস্য থ্রিলার।
আর অনেক কিছু জানলাম গল্পটা পড়ে। চেতনার এই সূক্ষ্মতম বিভাগগুলো জেনে বেশ ভালো লাগল, আরো পড়াশোনা করছি এটা নিয়ে। পড়ার সাথে সাথে আগ্রহটা ও বাড়ছে। খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয়। এর জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তবে একটা ভুল চোখে পড়ল। স্কটল্যান্ডের ওই শহরের নামের বানানটা “Edinburgh” হলেও উচ্চারণটা কিন্তু “এডিনবার্গ” নয়। ওটার সঠিক উচ্চারণটা হল “এডিনবরা/ এডিনবারা”!
আপনি সঠিক বলেছেন।আমিও এই কথাই ভাবছিলাম।আমরা এডিনবার্গ বলে ভুল উচ্চারণ করে গেলেও আসলে কথাটা এডিনব্রা।এছাড়াও অনেক স্কটরা গেলিক ভাষায় কথা বলে বলে উচ্চারণ অন্যরকম।শেষমেশ বাঙালি উচ্চারণটাই রয়ে গেছে।আপনার পড়ে ভালো লেগেছে শুনে আনন্দিত ,হলাম।বিষয়টা অনেক গভীর,আমি যতটা সম্ভব সরলভাবে ধরার চেষ্টা করেছি।অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে তাও।আপনি ইউটিউবে অনেক ডকুমেন্টারি পাবেন এই বিষয়ে।দেখে ভালো লাগবে।ভালো থাকবেন।লেখাটা পড়ার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
Concept r jonyo golpo ta porte bhalo laglo
Thank you Arnabda