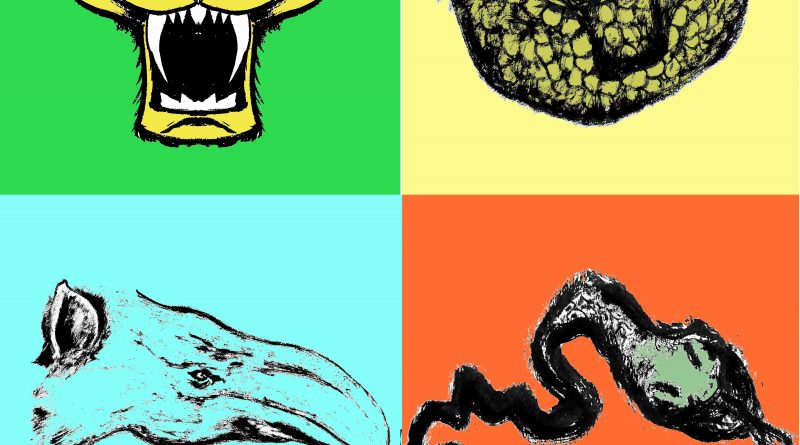মহাকাশযাত্রী বাঙালী
লেখক: প্রেমেন্দ্র মিত্র * দিলীপ রায়চৌধুরী * অদ্রীশ বর্ধন
শিল্পী: সৌরভ দে
ঘটনার অদ্ভূত যোগাযোগ জীবনে কখনো কখনো আশ্চর্যভাবে দেখা যায়। সকালবেলা কটা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ডাকে এসেছে। তন্ময় হয়ে তারই কয়েকটা নিবন্ধ ও আলোচনা পড়ছিলাম। মার্কিন একটি পত্রিকায় ‘কোয়াসার’ সম্বন্ধে অত্যন্ত চমৎকার একটি আলোচনা বেরিয়েছে। সেটি শেষ করে আরো দুটি পত্রিকার কোন নিবন্ধটি আগে পড়ব তাই নিয়ে তখন দ্বিধায় পড়েছি। একটি নিবন্ধ অ্যান্টিম্যাটার সম্বন্ধে। আর দ্বিতীয়টি পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন সংশ্লেষণ প্রকল্প এস-৬ নিয়ে, দুটির আকর্ষণই সমান।
মনঃস্থির করবার আগেই আমার স্নেহাস্পদ দুই সঙ্গী সঞ্জয় ও আকাশ সেন এসে উপস্থিত।
ঠিক এই সময়টিতে এই দুজনের আবির্ভাবও এক হিসেবে ঘটনার যোগাযোগ বটে, কিন্তু আসল যোগাযোগ এটি নয়। যথাসময়ে সে যোগাযোগের কথা বলছি।
টেবিলের ওপর খোলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকাটি দেখেই সঞ্জয় বলে উঠল, ‘কি পড়ছিলেন কাকাবাবু? ‘কোয়াসার’ সম্বন্ধে ওই আর্টিক্ল্টা’ত, সত্যই আজগুবি ব্যাপার।’
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম – ‘পড়েছ তুমি?’
‘হ্যাঁ, পড়েই ত আপনার কাছে আসছি, বৈজ্ঞানিকরা তো দেখছি ‘কোয়াসার’ নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছেন, তাঁদের এতকালের গড়ে তোলা সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝি আর হালে পানি পায় না। এই সেদিন ভারতীয় একজন বৈজ্ঞানিক ‘কোয়াসার’ বা রেডিও গ্যালাক্সি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে আগামী দশ বছরে জ্যোতর্বিজ্ঞান নব নব উত্তেজনার পথে অগ্রসর হতে পারে।’
‘কোয়াসার সম্বন্ধে এত উৎসাহ উত্তেজনার আসল কারণটা কি?’ জিজ্ঞাসা করল আকাশ।
‘এক কথায় এইটুকু মাত্র বলা যায়,’ বললে সঞ্জয়, – ‘যে আধুনিক বিজ্ঞান ‘কোয়াসার’ রহস্য উদ্ঘাটনে থই পাচ্ছেনা। দৃষ্টি-নির্ভর দূরবীণে যা নেহাৎ-ক্ষীণ নগণ্য তারার কণামাত্র, রেডিও দূরবীণে তারই প্রচন্ড তরঙ্গ ধরা পরার পর থেকেই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। গবেষণায় ও সন্ধানে এইটুকু জানা গেছে যে ‘কোয়াসার’ গুলি আমাদের ‘ছায়াপথে’র মতই কয়েকটি বিরাট নক্ষত্রমন্ডলী। তবে অন্ততঃ চারশো কোটি আলোকবর্ষ তাদের দূরত্ব। শুধু তাই নয়, সে নক্ষত্রমন্ডলীর তারাগুলিও অসামান্য কিছু, কারণ আমাদের ছায়াপথের মত প্রায় চল্লিশহাজার কোটি তারাময় পঞ্চাশটি নক্ষত্রমন্ডলীর মত আলোর জোর না হলে কোন ‘কোয়াসার’-এর ওই ক্ষীণ দ্যুতিও আমাদের কাছে পৌঁছত না। এছাড়া ‘কোয়াসার’-এর প্রধান রহস্যেরও কোনও হদিশ মিলছে না। ‘কোয়াসার’-দের আলো মাসে শতকরা দশ ভাগ বাড়ে কমে দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট ঘন গ্যালাক্সিরও ব্যাস অন্ততঃ একহাজার আলোকবর্ষ। বিজ্ঞানের এখনো যা অজ্ঞাত এমন কোন পরমাশ্চর্য প্রাকৃতিক নিয়মের লীলা এর ভেতর না থাকলে হাজার আলোকবর্ষব্যাপী নক্ষত্রমন্ডলীর এমন মাসিক স্পন্দন সম্ভব হয় না, বলে কেউ কেউ মনে করছেন।’
‘এই অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে অ্যান্টিম্যাটার –এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?’ –জিজ্ঞাসা করলেন আকাশ সেন।
‘অ্যান্টিম্যাটার !’ – সঞ্জয়ের গলায় একটু যেন কৌতুকের আভাস।
‘হ্যাঁ, অ্যান্টিম্যাটার – যাকে বিপরীত বস্তু বলা যায়। আমাদের জানা বিশ্বের পরমাণু গঠনের ঠিক তা উল্টো। যেমন অ্যান্টিম্যাটারের ইলেকট্রন পজিটিভ আর তার প্রোটন নেগেটিভ।’
‘যাক্ যাক্!’ সঞ্জয় এবার অধৈর্যের সঙ্গে বললে –‘অ্যান্টি-ম্যাটারের ব্যাখ্যা তোমার কাছে শুনতে চাইনি। আমি বলছি হঠাৎ অ্যান্টি-ম্যাটারের কথা এসূত্রে তোমার মাথায় এল কি করে? ‘কোয়াসার’ নিয়ে কেন বিজ্ঞান জগতে এখন এত হৈচৈ তাইত’ খানিক আগে জানতে চাইলে?’
‘তাত চাইলামই’, হেসে বললে আকাশ – ‘কোয়াসার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না। অ্যান্টি-ম্যাটার সম্বন্ধেও নয়, তবু জিজ্ঞাসা করছি। ‘কোয়াসার’ রহস্যের মূলে অ্যান্টিম্যাটার গোছের কিছু কি থাকা সম্ভব?’
‘কি সম্ভব, কি অসম্ভব – আমি ত’ ছার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরাও এখনো বলতে পারছেন না। কিন্তু হঠাৎ অ্যান্টিম্যাটারের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল কেন? দিব্যদৃষ্টি গোছের কিছু পেয়েছ নাকি?’
‘না, দিব্যদৃষ্টি পাইনি,’ আকাশ হেসে বললে- ‘পেয়েছি একটি অদ্ভুত চিঠি গতকাল। তাই পড়েই বলছি। চিঠি না বলে একতাড়া কাগজের প্যাকেটও বলতে পারো।’
আকাশ তার ফোলিও থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের টিকিট মারা একটি প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার বললে – ‘চিঠিটার সবই অদ্ভুত। যে লিখেছে, কলেজে পড়ার সময় তার সঙ্গে একটু পরিচয় হয়েছিল। তারপর আট দশ বছর তার কোন খবর জানি না। পড়াশুনায় খুব ভাল হলেও দারুণ খেয়ালী ছিল। বিজ্ঞানের কি একটা বৃত্তি পেয়ে বিদেশে চলে গেছ্ল এইটুকুই জানি। নামটা একটু অসাধারণ – অত্রি হাজরা।’
‘অত্রি হাজরা!’ – সঞ্জয়ের গলায় যেন একটু বিস্ময় ও কৌতূহল মেশানো।
‘হ্যাঁ, অত্রি হাজরা,’ আকাশ বললে ‘নামটার চেয়ে অদ্ভুত আজগুবি তার চিঠি। একটু পড়েই দেখুন না।’
তাই দেখতে যাচ্ছি এমন সময় নিচে থেকে আমার লেটারবক্সের কয়েকটা চিঠি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে গেল আমার ভ্রাতা। সেদিকে চেয়ে সঞ্জয় প্রথমেই বললে –‘আপনারও ত’ বিদেশ থেকে একটা প্যাকেট এসেছে দেখছি। স্ট্যাম্প ত’ দেখছি ব্রেজিলেরই।’
‘তাই নাকি!’ – বলে অবাক হয়ে প্যাকেটটা হাতে নিলাম, আর সেই মুহূর্তে প্রেরকের নামটার ওপরও দৃষ্টি পড়ল। নাম, অত্রি হাজরা।
একেই বলেছিলাম ঘটনার অদ্ভুত অবিশ্বাস্য যোগাযোগ। সুদূর ব্রেজিল থেকে একজন বাঙালী যে দুজনকে চিঠি লিখেছে তারা পরস্পরের পরিচিত শুধু তাই নয়, একই সময়ে একই জায়গায় উপস্থিত হয়ে এবং একই আলোচনায় মত্ত। যা নিয়ে ঘটনার এই যোগাযোগ, সেই চিঠি খুলে এবার একটু পড়লাম। আকাশ ঠিকই বলেছে। চিঠিগুলো সত্যি নামের চেয়ে অদ্ভুত।
আমাকে লেখা চিঠিটা প্রথমে যেন একটু আক্রমণ দিয়ে শুরু। আকাশ ও সঞ্জয়কে তাই পড়ে শোনালাম।
লিখেছে – যা আপনাকে লিখছি তা বিশ্বাস করতে পারবেন না জানি, আপনি কেন, পৃথিবীর জ্ঞানীগুনী বিজ্ঞানবিদেরাও ঐ সব কথা হেসে উড়িয়ে দেবে নিশ্চয়। কুপমন্ডুকের বিজ্ঞান নিয়ে এখনো আমরা সন্তুষ্ট। কি করে আমরা বিশ্বাস করবো পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য যুগান্তর ঘটে গেছে। ঘটে গেছে ২৪শে মার্চ ১৯৬১ তে। এই তারিখ কারুর কাছে নিশ্চয় স্মরণীয় নয়। মানুষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে তার পরের দিন ২৫শে মার্চ। প্রথম যেদিন একটা জীবন্ত কুকুর সমেত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে কক্ষপথে ছোঁড়া হয় রাশিয়া থেকে। কিন্তু একদিন আসবে যেদিন মানুষের মহাশূন্যে বিজয়ের প্রথম স্মরণীয় তারিখ বলে গন্য হবে ওই ২৪শে মার্চ। কেমন করে এ ব্যাপার সম্ভব হল যদি জানতে চান ভাল করে বোঝাতে পারবো না। ঘোড়ার ডাকে বা পায়রার সাহায্যে যারা সবচেয়ে দ্রুত খবর সেকালে পাঠাত, এখনকার বেতার তরঙ্গে সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে বার্তা প্রেরণের কথা কি তাদের বোঝানো সম্ভব ছিল?
প্রচন্ড রেডিও তরঙ্গের উৎসস্বরূপ ‘কোয়াসার’ নামে সুদূর নক্ষত্রমন্ডলীর কথা শুনেছেন বোধহয়। অ্যান্টিম্যাটার কাকে বলে তাও বোধহয় কিছুটা জানেন। ‘কোয়াসার’-এর সঙ্গে অ্যান্টিম্যাটারের রহস্যও যে জড়িত থাকতে পারে এই অনুমানের ওপর গবেষণা ও পরীক্ষা করতে গিয়েই আমাদের মহাকাশ যাত্রা ঘটে। কেমন করে ঘটে তা আমি নিজেও এখনও সম্পূর্ণ জানি না, জানবার চেষ্টা করছি মাত্র। না জানবার কারণ পরীক্ষার সাফল্য থেকে নয়, আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা থেকেই বিজ্ঞান আগেও অনেকবার নতুন অজানা আবিষ্কার উদ্ভাবনের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে।
আমাদের মহাকাশযাত্রার পিছনে বিরাট কোন আয়োজন ছিল না। ছিল না কোটি কোটি টাকার এলাহী কান্ড। না কোন আশ্চর্য রকেট সেন্টার, না লঞ্চিং প্যাড। নেভাডার মরুপ্রায় এক অঞ্চলের একটি নির্জন র্যাঞ্চে আমাদের সামান্য গবেষণাগার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গম্বুজের আকারের বিরাট একটি নিশ্ছিদ্র ধাতুর খোল মনে করুন। তারই মধ্যে বসে আমরা অ্যান্টিম্যাটার সম্বন্ধে নতুন একটি পরীক্ষা চালাচ্ছি। ‘কোয়াসার’ এর দুর্ভেদ্য রহস্যের কথা ভাবতে গিয়েই ডঃ শ্যাপিরোর মাথায় এ পরীক্ষার কথা এসেছে।
‘দাঁড়ান দাঁড়ান’ – সঞ্জয় বাধা দিলে। ‘ডঃ শ্যাপিরোর নামটা শুনেই এখন মনে পড়ছে। এই অত্রি হাজরা কে ত’ আমি চিনি। নামটা শুনে তাই প্রথমে চমক লেগেছিল।’
‘তুমিও চেনো!’ –একটু অবাক হয়ে বললাম। ‘কোথায় তোমার সঙ্গে পরিচয়?’
‘আমার পরিচয় হয়েছিল আমেরিকাতে’ – বললে সঞ্জয়।
‘’এ চিঠি কিন্তু লেখা ব্রেজিলের রায়ো-দ্য-জানেরিও থেকে। যা লিখেছে তাতে বিশ্বাস করাই শক্ত, মাথায় একটু ছিট আছে বলেও মনে হয়। আমায় লিখেছে যে এই মূল্যবান বিবরণ পাছে ডাকে খোয়া যায় এই ভয়ে অর্ধেকটা আমায় আর বাকি অর্ধেকটা আরেক-জনকে পাঠাচ্ছে।
আকাশ সেন বললে –‘সেই আরেকজন হলাম আমি। আমাকেও এই কথাই লিখেছে।’
বললাম- ‘বিবরণটা বিচার করার আগে এই অত্রি হাজরার একটু বিশদ পরিচয় পেলে ভালো হয়। অত্রি হাজরাকে আমেরিকায় কিরকম দেখেছ, তা যদি একটু জানাও সঞ্জয়।’
সঞ্জয়ের কথা
আমি তখন কেমিষ্ট্রিতে রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকায় সান ফ্রান্সিস্কোর কাছে বার্কলেতে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্ণিয়ায় গেছি। ফাঁক পেলে আশেপাশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে সেমিনার শুনতে যাই। কাছেই প্যাসাডেনায় ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। নানা পন্ডিত লোকে গিজগিজ করছে ওখানে। মাসে দুতিন দিন অদ্ভুত সব নতুন বিষয়ে বক্তৃতা হয়। নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রফেসরদের মুখে বক্তৃতা শোনার এরকম সুযোগ কজনের ভাগ্যে ঘটে।
সেদিন বোধহয় প্রফেসর ম্যালিনোভেস্কির বক্তৃতা ছিল। বিষয়ঃ ননইক্যুলিব্রিয়াম থার্মোডাইনামিক্স। অসম্ভব ভীড় হয়েছে। অতবড় অডিটোরিয়ামে তিলধারণের জায়গা নেই। বার্কলে থেকে আমরা কজন মোটরগাড়ীতে এসেছি। অফিস-কারখানা ফেরতা ভীড় ঠেলে পৌছতে এত দেরী হয়ে গেছে যে একেবারে পেছনের সারিতে বসা ছাড়া আর উপায় নেই।
অদ্ভুত বলতে পারেন প্রফেসর ম্যালিনোভস্কি – তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে প্রায় একঘন্টা কেটে গেছে। প্রশ্নোত্তরের সময়ই হঠাৎ চম্কে সজাগ হলাম। দেখি এক ভারতীয় ছোকরা মাঝখান থেকে উঠে দাড়িয়েছে। সুন্দর ঋজু উন্নত চেহারা, গায়ের রং শ্যামল – যেন বাংলাদেশের মাটির গন্ধ আছে বলে মনে হয়। স্পষ্ট সপ্রতিভ উচ্চারণে জিগ্যেস করলে – ‘প্রফেসর সব জায়গায় প্রচলিত থার্মোডাইনামিক্সের আইন নাও থাকতে পারে?’
প্রবীণ অধ্যাপকের প্রশস্ত কপালে তিনটি খাঁজ পড়লো –‘হোয়াট ডু ইউ মীন? আমি ত’ এমন কোনও নজীর জানি না।’
‘আমি জানি’ – ছেলেটি দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সুরে বললে।
‘তাই নাকি? সেই স্ট্রেঞ্জ জায়গাটা কোথায়?’ এ প্রশ্নের জবাবে ছেলেটি বললে –‘এখান থেকে চারশো কোটি আলোক বছর দূরে একটি রেডিও গ্যালাক্সিতে!’
কথাটা এতদূর অবিশ্বাস্য, এত কষ্টকল্পিত যে প্রথমে বিস্ময়ে আবিষ্ট হলেও কয়েক মুহূর্ত পরে একটা বিরাট পরিহাস মনে করে সকলে হাসির অট্টরোলে ফেটে পড়লো।
‘হাসবেন না, শুনুন!’ – ছেলেটির গলা শুনে সকলে চুপ। সমস্ত অডিটোরিয়াম নিস্তব্ধ – একটা আলপিন পড়লেও শোনা যায়।
‘থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড ল অনুযায়ী এনার্জি উচ্চতর অবস্থা থেকে নীচের দিকে যায়। কিন্তু রেডিও গ্যালাক্সিতে তার ঠিক উল্টোটা ঘটেছে বলে মনে হয়।’
ওর কথা শুনে সবাই যখন অবিশ্বাসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে এবং কেউ কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে সকৌতুকে ওকে দেখছে, এমন সময় সামনের সারি থেকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমার পাশ থেকে বন্ধু ট্র্যাভিস ফিস্ফিস্ করে কানে কানে বললে –‘উনি প্রফেসর শ্যাপিরো –পালোমার অবজারভেটরির ভীষণ নামকরা লোক।’
প্রফেসর শ্যাপিরো তখন বলতে শুরু করেছেন –‘আমাদের তরুণ বন্ধুটি ঠিকই বলেছেন। মহাকাশে কোনও কোনও গ্যালাক্সিতে আণবিক বিস্ফোরণের পর বিপুলসংখ্যক বস্তুকণা দেখা দেয়। এইসব বস্তুকণার শক্তি জন্মের মুহুর্তে কয়েক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি। প্রফেসর ম্যালিনোভস্কির থার্মোডাইনামিক্স অনুযায়ী ঐসব বস্তুকণার সঙ্গে অন্যান্য বস্তুকণার সঙ্ঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়ে শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবার কথা। অথচ তা না হয়ে কোন এক অমোঘ নিয়মে ওদের শক্তি বাড়তে বাড়তে সহস্র মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি পৌঁছয়। এর কোনও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে পারেন?’
প্রফেসন ম্যালিনোভস্কি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর সংক্ষেপে বললেন –‘না আমাদের গ্যালাক্সিতে এধরণের ঘটনার নজীর নেই।’
বলা বাহুল্য এরপর প্রশ্নোত্তর আর জমলো না। সেমিনার ভাঙ্গতেই করিডরে এই চাঞ্চল্যকর ভারতীয় নায়কটিকে পাকড়াও করলুম।
‘আপনি বাঙালী?’
আমার এই সরাসরি প্রশ্নে ছেলেটি মোটেই চমকালো না। পাল্টা আক্রমণ করলে –‘তবে আপনি কি ভেবেছিলেন আমি মেক্সিকান! খাঁটি কোলকাতার লোক। মেডিক্যাল কলেজের উল্টো দিকে মধুগুপ্ত লেনে আমার বাড়ি।’
ভালই হলো, বাংলা কথা বলবার জন্য আমার পেট ফুলছিল, আলাপটা খুব তাড়াতাড়ি জমে গেল বলতে হবে। ট্র্যাভিসদের বললুম আমাকে প্যাসাডেনায় রেখে বার্কলে ফিরে যেতে। আমি বাসে করে ফিরে যেতে পারবো।
আধঘন্টা বাদেই বুঝতে পারলুম অডিটোরিয়ামে প্রথম দেখার পর যা মনে হয়েছিল সে ধারণাটা বিন্দুমাত্র ভুল নয়। ছেলেটা একটা জিনিয়াস, কিন্তু বদ্ধ পাগল। বছর তিন-চার হলো ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মাউন্ট উইলসন ও পালোমার অবজারভেটরিতে গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হিসেবে এসেছে। নাম- অত্রি হাজরা। নামটা বলার পর বুঝতে পারলাম কোলকাতা কাগজে এ’নাম কয়েকবার দেখেছি। অঙ্কে ঈশানস্কলার, তারপর এম.এ.-তেও ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট। একটু সসম্ভ্রমেই প্রশ্ন করলাম – ‘এখানে আপনার পি.এইচ.ডি.’র কাজ শেষ হয়ে গেছে ত’?’। হো হো করে হেসে উঠলো। সে হাসি আর থামতেই চায় না। হাসির দমকটা থামলে বললে – ‘এরা বলে কি খালি থিসিস দিলেই চলবে না। পি.এইচ.ডি. হতে গেলে লেখা পরীক্ষা পাশ করতে হবে। ভোরবেলা আটটায় গিয়ে ঐ সব বোরিং মাষ্টারদের পড়া শুনবে কে? তার ওপর কোন জন্মেই আমি ভোরে উঠতে পারি না। ফলে ঐ ছাতার পি.এইচ.ডি. আমার মাথায় উঠলো না।’
রাত হয়ে যাচ্ছে। রাত্তিরের খাওয়াটা কোথায় খাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে বললুম – ‘এখানকার ক্যাফেটেরিয়া কিরকম? কিছু খেতে টেতে পাওয়া যাবে এখন?’
কতকটা বকুনির সুরে বললে- ‘ঐ সব ছাইপাঁশ আমি গিলতে পারি না। আর দ্যাখো বাপু ঐ সব মার্কিনি কেতা ছাড়ো। চলো, আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ভাত মাছের ঝোল খাবে।’
অ্যাপার্টমেন্টটা অসম্ভব নোংরা ও অগোছালো। মেঝের উপরে ও টেবিলে চারিদিকে রাশিকৃত অঙ্কের বই ও কাগজে কষা আঁকজোক ছড়ানো। এক দিকে একটা গেলাসে কবেকার একটা শুকনো গোলাপ ফুল। ম্যান্টলপিসের উপর কালীমূর্তির একটা কাঠের ফলক।
খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে কৌচে এসে আরাম করে বসা গেল। এরকম নির্ভেজাল আড্ডা মারবার সুযোগ কোলকাতা থেকে আসবার পর একদিনও পাওয়া যায় নি।
‘আচ্ছা, পি.এইচ.ডি. যদি না করো তবে কতদিন থাকবে আর?’
আমার কথা শুনে অত্রি যেন একটু ক্ষেপে গেল –‘হু! মনে হচ্ছে তোমাকে কে যেন আমার গার্জেনি করতে পাঠিয়েছে। আমার যতদিন খুশি থাকব।’
ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম –‘আরে না! না! আমি তা বলিনি, মানে তোমার ফিউচার প্ল্যান কি তাই জানতে চাইছি।’
‘প্ল্যান, হো হো!’ -আবার সেই দিলখোলা হাসি- ‘সেদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়েভলেংথের ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের ভেলসিটি মাপছিলাম। তুমি ত’ জানো সবাই ধরে নিয়েছে আলোর গতি ও ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের গতি সমান। কিন্তু অকাট্য প্রমাণ যোগাতে পারেনি কেউ। কষ্ট করে বিভিন্ন তারা থেকে অঙ্ক কষে যখন প্রমাণ করলুম যে বেতার তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গ মূলতঃ একই বেগে চলছে, ততদিনে ছ-মাস কেটে গেছে, আর সবাই আমাকে পাগল ভেবে মুখ টিপে হাসছে।’
‘জানি তুমি কি ভাবছো। তাতে দুনিয়ার কি লাভ হলো, এই তো? এখানেই তোমাদের গন্ডগোল। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, রামানুজ- এঁদের ধৈর্য তোমাদের নেই। চাও তাড়াতাড়ি পি.এইচ.ডি. করে গিয়ে মোটা মাইনের চাকরীতে বসতে।’
কথায় কথা বেড়ে যায়। কখন যে এইসব অদ্ভূত গল্পের মধ্যে সে রাত পুইয়ে গেছে তা জানতেও পারিনি।
ভোরবেলা বাসে বার্কলে ফিরে এলাম। তারপর সারা সপ্তাহ যেন চুম্বকের মত প্যাসাডেনা আমাকে টানতে লাগলো। শনিবারের আগে আর যাওয়ার সুবিধে হোল না।
দেখি অত্রির অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা। একটা জ্যানিটর ঘরটা সাফ-সুতরো করছে। বই খাতাপত্তর কিছু নেই। আমার একহপ্তা আগেকার চেনা মানুষটির কোনও চিহ্ন নেই।
‘কি হলো? লোকটি গেল কোথায়?’
জ্যানিটর আমার মুখের দিকে তাকালে, তারপর বললে-‘দ্যাখো বাছা, আমার কাজ ঘর সাফ করা, কোন ভাড়াটে কখন আসছে কখন যাচ্ছে তা খোঁজ রাখা আমার কাজ নয়। যদি তোমার দরকার থাকে ত’ ল্যান্ডলেডীকে জিগ্যেস করো।’
নীচে নেমে ল্যান্ডলেডীর ঘরে নক করলুম।
সাড়া এলো-‘ইয়েস, কাম ইন।’
‘আচ্ছা বলতে পারেন, আপনার তেরো নম্বর ঘরের ভাড়াটে মিঃ হাজরা কোথায় গেলেন?’
ভদ্রমহিলা কি একটা ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন-‘কিছু মনে করবেন না, ইউ ইন্ডিয়ানস আর ভেরী স্ট্রেঞ্জ!’ গত পরশুদিন মিঃ হাজরা সন্ধ্যের দিকে আমার হাতে চারমাসের আগাম ভাড়া দিয়ে বললেন-‘আমি আপনার ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। সেসনের মাঝখানে নতুন ভাড়াটে না পেলেও যাতে আপনার কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্য আগাম ভাড়া রেখে গেলাম। বিদায়, এই বলে ঝড়ের মত উধাও। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, চিঠি রিডাইরেক্ট করার ঠিকানা কি- কিছুই বলে গেল না।’
ওখান থেকে বেরিয়ে আমি অবজারভেটরীতে গেলাম। তারাও কিছুটা হতভম্ব। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, অত্রিও নেই- সেই সঙ্গে প্রফেসর শ্যাপিরোরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা এর পরের বিবরণ আপনাদের চিঠিতে নিশ্চয় কিছু আছে।
হ্যাঁ আছে। তবে বেশী কিছু নয়, ডঃ শ্যাপিরোর সঙ্গে যোগ দিয়ে কিভাবে নেভাডার এক নির্জন র্যাঞ্চে একটি গোপন পরীক্ষাগার তারা তৈরী করে তারই সামান্য বর্ণনা দিয়ে অত্রি ২৪শে মার্চের সেই বিশেষ ঘটনার কথাই লিখেছে। কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের পরীক্ষায় সেদিন অকস্মাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমে তাদের মনে হয় বুঝি তাদের বিশাল ধাতুর খোলটা কোন বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড এক ঝাঁকুনির সঙ্গে শরীরের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় তারা কিছুক্ষণের জন্য অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় কতক্ষণ কাটে তারা জানে না। জ্ঞান হবার পর বিশেষ উপাদানে তৈরী ধাতব খোলের স্বচ্ছ দুটি জানালা খুলে তারা যা দেখতে পায় তার কোন মানে বুঝতে পারে না। নেভাডার মরুপ্রায় প্রান্তর নয়, তাদের চারিদিকে যেন শূন্য কালো আকাশ, আর সে আকাশে যেন অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। শ্যাপিরোই প্রথম ব্যাপারটা অনুমান করে বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠেন-‘একি! দেশ কালের কোন অজানা রহস্য প্রক্রিয়ায় আমরা যে মহাশূণ্যে চলে এসেছি।’
আমাদের পরীক্ষার কোন ভুলে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তাইতেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এ ধাতব খোল বোধ হয় অ্যান্টিম্যাটার এর গুণ পেয়েছে। তাইতেই সম্ভব হয়েছে এ অবিশ্বাস্য ব্যাপার।
এইভাবে মহাশূণ্যে কতক্ষণ তাদের কেটেছে তার হিসাব তারা রাখতে পারেনি। সময়ের হিসাবও বুঝি সে মহাশূণ্যে আলাদা। বহুক্ষণ বাদে আলোর বুদ্বুদ ভরা আকাশের চেহারা বদলেছে। ডঃ শ্যাপিরো উত্তেজিত ভাবে বললেন, ‘এবার স্বাভাবিক দেশকালের রাজ্যে ফিরছি। ওই ত’ একটা গ্রহের দিকেই যেন আমরা নামছি মনে হচ্ছে।’
তাদের নিঃশ্বাসের হাওয়া তখন ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং এ গ্রহে নিরাপদে নামতে পারলেও পৃথিবীর মত বাতাস পাবে কিনা তাই তখন চিন্তা।
খুব নিরাপদে নামা হয়নি। ধাতব খোলটা বেশ জোরেই আছড়ে পড়ে কিছুটা ভেঙেছে। ডঃ শ্যাপিরো একটু আহত হয়েছেন।
বাইরে বেরিয়ে এসে এবার অত্রি হাজরা লিখেছে-
* * *
এ কোন গ্রহে এলাম আমি?
যে দিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি বিস্ময়কর মোটা থামের মত গাছ। বহু উঁচুতে ডাল-লতাপাতার ঘন বুনুনির ফাঁকে ফাঁকে কালো আকাশের বুকে তারার চুমকির মত মধ্যে মধ্যে ঝিকমিক করে উঠছে আলো …… এ গ্রহের সূর্যের আলো!
এযে পৃথিবীর মতই। বুক ভরে শ্বাস নিলাম আমি। কই, না তো? কোন অসুবিধা নেই। পৃথিবীর মতই তেজালো এখানকার বাতাস … তফাৎ শুধু ঝাঁঝালো গন্ধে …
অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সৌরজগত থেকে এত যোজন পথ পাড়ি দিয়ে যে শেষকালে পৃথিবীর মতই আর একটি গ্রহে পা দিতে পারবো তা কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম?
আকাশযানের পাশেই আহত ডক্টর শ্যাপিরোকে শুইয়ে রেখে পায়ে পায়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছিলাম। নতুন গ্রহ দেখার আনন্দে খেয়াল ছিল না কতদুর এসেছি।
চমক ভাঙ্গলো একটা বিদঘুটে আওয়াজ শুনে। শব্দটা আসছিল পেছন থেকে। ঘুরে দাঁড়িয়েই দারুণ ভয়ে অবশ হয়ে গেল আমার সমস্ত শরীর।
আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক ফালি জমির ওপরে। একটু দুরেই কালো পর্দার মত ঘন বন। বহু উঁচু থেকে লতাগুলো নামতে নামতে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। এমনি একটা লতা-গুঁড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল বিচিত্র একটা জানোয়ার।
এরকম সৃষ্টিছাড়া জীব এ গ্রহে দেখতে পাবো, তা ভাবতেই পারিনি। সৃষ্টিকর্তা যেন নিছক রঙ্গ করবার জন্যই হাতি আর গন্ডারকে একসঙ্গে জুড়ে ছেড়ে দিয়েছেন এ গ্রহের জঙ্গলে। গন্ডারের মতই তার পিছনের অংশ, তবে বর্মপ্যাটার্নের নয়- মসৃণ। বেঁটে বেঁটে চারটে পা। কিন্তু অদ্ভূত তার মুখটা। গন্ডারের খড়্গের বদলে সমস্ত নাকটাই গড়ুরের ঠোঁটের মত বেঁকে সরু হয়ে নেমে এসেছে। যেন হাতির শুঁড় যাদুমন্ত্রবলে গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে।
বিদঘুটে আওয়াজটা হাঁসজারু মার্কা এই জন্তুটার গলা থেকেই বেরোচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো, চতুস্পদ হলেও ভিন্ গ্রহের এই জীবটি মানুষের মতন বুদ্ধিমান কিনা, তা যখন জানা নেই, তখন সময় থাকতেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেওয়া ভাল।
তক্ষুনি জানোয়ারটার দিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলাম। আরও অস্থির হয়ে উঠলো হাঁসজারু। তারপরই মাথা নিচু করে ধেয়ে এল আমাকে লক্ষ্য করে।
পেছন ফিরেই উর্ধধশ্বাসে দৌড়ালাম। বনের মধ্যে ঢুকেও থামতে সাহস হলো না। কাঁটায় জামাকাপড় ছিঁড়ে, বেশ কয়েকবার ঝোপেঝাড়ে আছাড় খেয়ে শেষপর্যন্ত যুতসই একটা লতা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডালে উঠে পড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ক্ষ্যাপা দানোর মত মাটি কাঁপিয়ে তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল হাঁসজারু। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ।
হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ঘেমেনেয়ে গেছিলাম ছুটোছুটির ফলে। নতুন গ্রহে প্রথম জীবটির ব্যবহার দেখে মনটাও খিঁচড়ে গেছিল। নেমে এসে আকাশযানের দিকে যেতে গিয়ে বুঝলাম, সর্বনাশ হয়েছে।
আমি পথ হারিয়েছি। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে গিয়ে খেয়াল নেই কোনদিকে ফেলে এসেছি আমাদের আকাশযান।
কিন্তু ভয়ে দিশেহারা হলে তো চলবে না। আকাশযানে এক্ষুনি আমাকে ফিরতেই হবে। আহত ডঃ শ্যাপিরো আকলা রয়েছেন সেখানে।
কোনদিকে যাই? শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে বনটা একটু ফাঁকা মনে হলো যেদিকে, সেইদিকেই পা বাড়ালাম।
যতই এগোই ততই বাড়তে থাকে আমার বিস্ময়। নিবিড় অরণ্য, অথচ নিস্তব্ধ নয় মোটেই। অজস্র পাখীর ঐকতানে তা মুখরিত। ভগবান এদের সব দিয়েছেন, দেননি কেবল সুধাকন্ঠ। কালো কুৎসিত কোকিলের কন্ঠে যে মিষ্টতা, টেরোড্যাকটিলের চিৎকারের মত এদের কর্কশ ডাকে তার রেশমাত্র নেই।
আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল বনভূমি। আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ব্যাপার কি?
এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে যা দেখলাম, মাথার চুল খাড়া করার পক্ষে তাই যথেষ্ট।
হাত পনেরো দূরে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। ঠিক মাঝে নিঃসীম আতংকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে একটা ভারী সুন্দর পাখী … কাঁচের অপলক মণির মত চক্চক্ করছে দুটি চোখ, থিরথির করে কাঁপছে গায়ের পালক … আর…
আর…এক্টু দুরেই কিলবিলিয়ে এগিয়ে আসছে একটা লতা!
চলমান লতা! পরক্ষণেই শিউরে উঠলাম আমি। লতা নয়, সাপ! যেমন মোটা, তেমনি লম্বা! ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়েছে শুধু খানিকটা দেহ-সেইটুকুরই দৈর্ঘ্য দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল আমার দুই চক্ষু!
সাপ, না, নতুন কোন দৈত্য-জীব? সাপ কি এতবড় হয়? এ গ্রহে জীবনের বিবর্তন কি তাহলে হুবহু পৃথিবীর মতই? বয়স উত্তাপ আয়তন আর গড়ন পৃথিবীর মত হলে যে কোনো গ্রহে কিম্ভূতকিমাকার জীব নাও থাকতে পারে- জ্যোতির্বিজ্ঞানী হারলো শ্যাপলের এই থিওরী কি সত্য বলেই প্রমাণিত হলো?
আর সময় নষ্ট করা যায় না। অতিকায় সাপ থাকুক তার সুন্দর খাবার নিয়ে, সূর্য হেলে পড়েছে, আলো নেভবার আগেই পৌঁছতেই হবে।
কিন্তু কোথায় আমাদের সেই একমাত্র নিশ্চিত আশ্রয়? হাঁটছি তো হাঁটছিই। পা টন্-টন্ করছে। ক্ষত-বিক্ষত চামড়া জ্বালা করছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে-কিন্তু বনের শেষ তো নেই? নেই সেই চত্বর যার মাঝে রেখে এসেছি আমাদের আকাশযান।
হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটা খস্ খস্ শব্দ আসছে না?
দাঁড়িয়ে যেতেই শব্দটাও থেমে গেছিল। ঝোপঝাড় ঠেলে যাওয়ার শব্দ নয় তো?
পা বাড়ালাম…একটু পরেই আবার সেই শব্দ…খস্…খস্…খস্! কে যেন এগিয়ে চলেছে ঝোপের মধ্য দিয়ে।
ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। হিংস্র প্রাণী, না ধীমান প্রাণী-এ কার পাল্লায় পড়লাম এবার?
প্রায় একশো ফুট উঁচু একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। সাদাটে গুঁড়ির ছালে অজস্র ফাটল। হাঁচড় পাঁচড় করে এই ফাটলগুলোতে পা রেখেই উঠে পড়লাম সব চাইতে নীচের ডালটাতে।
আশ্চর্য! খস্ খস্ শব্দটা কিন্তু এবার থামেনি। একইভাবে এগিয়ে আসছিল এইদিকে। তারপরেই ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভূত প্রাণী!
চতুস্পদ প্রাণী। মধ্যযুগে নাইটরা যেরকম বর্ম পরতো, অনেকটা সেই ধরণের কারুকাজ করা বড় বড় শক্ত হাড়ের খোলা সাজানো সমস্ত শরীরে। ল্যাজেও সারি সারি আংটির মত হাড়ের বর্ম। ছুঁচোলো মুখটা মাটির দিকে নামিয়ে এহেন প্রাণীটাই বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে।
এরপরেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটলো পরপর কয়েকটি ভয়ংকর ঘটনা।
বর্মপরা প্রাণীটা খুব সম্ভব কৌতূহল বশেই পিছু নিয়েছিল আমার। কিন্তু অকস্মাৎ যেদিকে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই-দিক দিয়েই বেরিয়ে এল আর একটা চারপেয়ে জানোয়ার।
পলকের মধ্যেই স্প্রিং-এর বলের মত লাফিয়ে উঠে শূণ্যপথে অতবড় জানোয়ারটা এসে পড়লো বর্মপরা প্রাণীটার ওপর।
পরমূহুর্তেই ঘটলো সেই ম্যাজিক। আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চকিতের মধ্যে বর্মওলা অতবড় প্রাণীটা গোল বলের মত হয়ে গেল। ল্যাজ-মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে-কঠিন বর্ম মোড়া অতিকায় একটা বল গড়িয়ে গেল মাটির ওপর দিয়ে।
নতুন জানোয়ারটার ক্রুদ্ধ গর্জনে থরথর কেঁপে উঠলো বনভূমি। এতক্ষণে ভালো করে দেখতে পেলাম। জিঘাংসাভরা হাড়িঁর মত মুখ…সর্বাঙ্গে হলদে চামড়ার ওপরে অজস্র কালো ফুটকি।
হুংকার আর আঁচড় পরেও যখন বর্মভেদ করে উঁকি দিল না বেরসিক প্রাণীটা, তখন রাগে গড়্ গড়্ করতে করতে একলাফে একটা গাছের ডালে গিয়ে উঠলো হিংস্র শ্বাপদ টা …সেখান থেকে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল পাতার আড়ালে। আমিও নেমে এসে আবার রওনা হলাম আকাশ-যানের খোঁজে।
কিছুক্ষণ পরেই সূর্য মুখ লুকোলো দিগন্তে। আরও একটু পরে দ্রুত ছড়িয়ে পরতে লাগল সন্ধ্যার আঁচল। এখানে-সেখানে উঁকি দিল তারার চুমকি।
শ্বাপদসঙ্কুল এ অরণ্যে আর হাঁটা উচিত নয়। শ্রান্ত অবসন্ন দেহটা কোনমতে টেনে তুললাম একটা গাছের ডালে। ভেবেছিলাম রাতটা সেখানেই কাটাবো ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত — কিন্তু তার আগেই দেখলাম এক অসম্ভব দৃশ্য!
দূরে…অনেকদূরে…গাছপালার ফাঁক দিয়ে আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম ঢিবির মত উঁচু একটা জমাট অন্ধকার…
একি দেখছি আমি? বিচিত্র গ্রহের নতুন কোনো রহস্য নয় তো?
অত্রি হাজরার বিবরণ এরপর সংক্ষিপ্ত হলেও বিস্ময়কর। দূরের আলো আর ছায়ামূর্তিগুলির সন্ধানে গিয়ে সে বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছে। অজানা কোন গ্রহের প্রাণী নয়, সেগুলি মানুষ। তারা সেখানে একটি ম্যাঙ্গানীজ খনিতে কাজ করে। খনির ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে সে জেনেছে যে জায়গাটা ব্রেজিলেরই একটি পার্বত্যবন্য অঞ্চল। ব্রেজিলের টাপির, আর্মাডিলো, অ্যানাকোন্ডা ও জাগুয়ারকেই সে অজানা গ্রহের প্রাণী মনে করেছে।
সে তখন বুঝেছে যে কোনো অজানা রহস্য প্রক্রিয়ায় তাদের ধাতব আধার মহাশূণ্যে পৌঁছে আবার পৃথিবীতেই নেমে এসেছে। অজানা রহস্য প্রক্রিয়া কি হতে পারে ডঃ শ্যাপিরোর সঙ্গে গোপনে সেই গবেষণাই এখন সে করছে লিখেছে।
‘কিন্তু এ কাহিনী কি বিশ্বাস করার মত?’ –জিজ্ঞাসা করলে সঞ্জয়। ‘মহা আজগুবি গল্পই আমাদের ওপর চালিয়ে দিয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।’
‘আমারও তাই, মনে হচ্ছে,’—বললে আকাশ, — ‘কলেজ জীবনে অত্রি গল্প লিখত এখন মনে পড়ছে। কে জানে সে রোগ হয়ত ওর কাটেনি।’
কঃসঃ – মহাকাশযাত্রী বাঙালী গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আশ্চর্য! পত্রিকায়। লেখক ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী-র কন্যা শ্রীমতী যশোধরা রায়চৌধুরীর অনুমতিক্রমে এখানে প্রকাশিত হল। গল্পটি টাইপ করে ডিজিটালাইজড করতে সাহায্য করেছেন দোয়েল বর্মণ। গল্পটি আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ৩রা মার্চ সাহিত্য-বাসর অনুষ্ঠানে।
Tags: অদ্রীশ বর্ধন, ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী, পুনঃপ্রকাশিত কল্পবিজ্ঞান, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৌরভ দে