দ্বিতীয় জগত
লেখক: অধরা বসুমল্লিক
শিল্পী: কৌশিক সিনহা চৌধুরী
অপরূপ সুন্দর একটা সরোবর। আর সেই সরোবর ঘিরে পাথর আর বালি, তারপরে তৃণভূমি। আসলে এটা একটা ছোটো উপত্যকা। পাহাড়ের মালায় ঘেরা। পাহাড়গুলো সব বালিপাথরের পাহাড়, হলুদ বালিপাথর। তাই পাহাড়গুলোকে সোনার পাহাড় বলে মনে হয়।
একটা পাহাড় থেকে নেমেছে ছোটো একটা ঝর্ণা, সেটা নদী হয়ে বয়ে এসে হ্রদে মিশেছে। পাহাড়ের নাম সুবর্ণগিরি, নদীর নাম ভদ্রা আর হ্রদের নাম নীলতারা।
সমতলভূমি বিস্তৃত হয়ে দূরে দিগন্তরেখায় ধোঁয়াটে হয়ে মিলিয়ে গেছে। বৃষ্টি এখানে সত্যি খুব উপভোগ্য দৃশ্য। পাহাড়ের মাথা থেকে দুলতে দুলতে নেমে আসে মেঘেরা, বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে দূরের মাঠের শেষে মিলিয়ে যায়।
এটা আসলে একটা কৃত্রিম জগৎ, লোকেরা বলে Ecosphere2, দ্বিতীয় জীবমন্ডল। বিভিন্ন বিষয়ের বহু বিজ্ঞানী একত্রিত হয়ে এটা তৈরী করেছেন। খুবই খরচবহুল এই প্রকল্প।
কিন্তু একটা জিনিস এঁদের জন্য খুবই সুবিধাজনক ছিল, এঁদের যে দলনেতা, সেই বিজ্ঞানী একজন প্রচন্ডরকম ধনী ব্যক্তি। প্রধানতঃ তাঁর জেদেই এগিয়েছে এই প্রকল্প। একেবারে প্রথমে যখন এর সাফল্য সম্পর্কে কারোর কোনোই আশা-ভরসা ছিল না, তখন এই বিজ্ঞানীর অনমনীয় মনোভাবই এই প্রকল্পকে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়েছিল। তারপরে যতো দিন গিয়েছে ততই আরো বেশী লোকেরা যোগ দিয়েছেন, আরো বেশী অর্থ এসেছে – জোরদার হয়ে জমে উঠেছে পরিকল্পনা।
এই বিজ্ঞানী পেশায় ছিলেন মাইক্রোবায়োলজিস্ট। খুব অল্প বয়সেই নিজের কোম্পানী বানিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন আর অল্প সময়ের মধ্যেই খুব সাফল্য পেয়েছিলেন, তাই মধ্য-চল্লিশেই তিনি এত অর্থের মালিক।
ডঃ মহেন্দ্র ভৌমিকের এই সাফল্যের গল্প প্রায় রূপকথার মতো শোনায়। প্রথম জীবনে অত্যন্ত দরিদ্র ঘরে জন্মেছিলেন, শুধুমাত্র নিজের মেধা সম্বল করে লড়ে যেতে হয়েছিল তাকে। সেখান থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই এত উঁচুতে উঠে আসার গল্প সেই কুটির থেকে কোটিপতি হবার গল্পের মতই।
তবে কিনা নিজের পারিবারিক জীবন বলতে কিছুই নেই তাঁর। বহুবছর শুধু কাজ নিয়েই মেতে থেকেছেন, বিয়ে করার পর্যন্ত ফুরসত হয়নি তাঁর। এই মধ্য-চল্লিশে পৌঁছে মাত্র কিছু বছর আগে বিয়ে করেছিলেন প্রথম জীবনের সহপাঠিনী সোফিয়াকে। ওঁদের একটিমাত্র সন্তান, ছেলে। ছেলের নাম প্রত্যুষ। ও জন্মানোর পরেই অসুখে মারা যান সোফিয়া।
ছেলেটা মানুষ হচ্ছে পরিচারিকাদের হাতেই। ওর বাবার তো হাতে একেবারেই সময় নেই কিনা। তিনি তাঁর প্রোজেক্ট নিয়েই মেতে আছেন, এই প্রোজেক্টই তার ধ্যানজ্ঞান। দ্বিতীয় পৃথিবী বানাতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের পৃথিবীকে প্রায় ভুলতে বসেছেন।
Eco-2 প্রোজেক্ট যখন খাতাকলম থেকে সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপায়িত হতে শুরু করে, তখন প্রত্যুষের মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়স। কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সবে যেতে শুরু করেছে।
ওর স্মৃতিতে কিন্তু বাবা বা মা কারুরই জোরালো অস্তিত্ব নেই। শুধু রয়েছে সোফিয়ার হাসিমুখ সুন্দর একটি ছবি, বিয়ের পরে পরেই তোলা হয়েছিল ছবিটা, তখনো প্রত্যুষ হয় নি। বাবার শোবার ঘরের দেয়ালে টানানো এই ছবিই ওর কাছে মায়ের আভাস। যে পরিচারিকা ওকে দেখাশোনা করে সে একটি তরুনী, নাম স্টেলা, ছটফটে স্বভাবের সুন্দর একটি মেয়ে। এই কাজ নেবার আগে ওর নিজের বয়ফ্রেন্ড ছিল, নিজের সংসার তৈরীর দিকেই এগোচ্ছিল ও। কিন্তু এখানে কাজ নেবার পর এই ফুটফুটে সুন্দর ঝকঝকে বাচ্চাটাকে দেখে সে এত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল যে আগের সমস্ত সম্পর্ক শিকেয় তুলে দিয়ে শুধু একে নিয়েই দিনরাত মেতে রইলো। যেভাবে সে এই ছেলের যত্ন শুরু করলো সেভাবে নিজের সন্তানেরও কেউ করে না। ডঃ ভৌমিক ছেলের দায়িত্ব স্টেলার হাতে দিয়ে নিজে Eco2 নিয়ে মেতে আছেন।
এই দ্বিতীয় জীবমন্ডল সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী থেকে পৃথগীকৃত। অতি উঁচুদরের স্বচ্ছ পদার্থের আবরণে ঢাকা। এই আবরন অর্ধগোলকাকার আর অনেক বড়ো। তাই এই দ্বিতীয় জীবমন্ডলের ভিতর থেকে আকাশকে ঠিক আমাদের চেনা আকাশের মতই দেখায়।
এই দ্বিতীয় পৃথিবীতে রাখা হয়েছে শুধু তৃণভোজী জীবেদের, কোনো মাংসাশী জীব নেই এখানে। বহু ধরণের গাছপালা রয়েছে আর রয়েছে বহু ধরনের পাখী ও মৌমাছি, বোলতা, প্রজাপতিজাতীয় উপকারী কীটপতঙ্গ।
এখানে সব কাজ করে রোবটেরা। তারাই জমি চাষ থেকে শুরু করে ফসল তোলা ঝাড়াই বাছাই, তা থেকে খাবার তৈরী সব করে। অফুরন্ত সৌরশক্তিতে শক্তিমান তারা।
মানুষ বলতে এখানে আছেন ঠিক দশজন দম্পতি। তারা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এখানে বাস করছেন। সবাইই Eco2 প্রোজেক্টের বিজ্ঞানী। এই কুড়িজন মানুষ পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন। এঁরা আর এখান থেকে বেরোতে পারবেন না, শুধু বাইরের বিজ্ঞানীদলের সঙ্গে তাদের ফোনে আর কমুনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে।
প্রথমেই বলা যাক সুতনু আর সীবলীর নাম। তারা এই দম্পতিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আর তারাই সবচেয়ে আগে এসেছে এখানে। ওদের বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর হতে চললো। সুতনু আর সীবলী দুজনেই পদার্থবিদ ও ইঞ্জিনিয়ার, রোবট বিশেষজ্ঞ ওঁরা।
এরপরে আসে ডেভিড আর রীতার নাম। ডেভিড মাইক্রোবায়োলজিস্ট আর রীতা কাজ করে সাইবারনেটিকস নিয়ে। ওদের বিয়ে হয়েছে দু’বছর আগে, ওরা এখানে এসেছে সুতনু আর সীবলীর ঠিক পরে পরেই। তারপরে আসে উপমন্যু আর মনীষা, তাদের দুজনের গবেষনাই জেনেটিক্স এ। ওদের পরে এসেছে ঋতুপর্ণ আর মার্থা। ঋতুপর্ণ কাজ করে সৌরশক্তি নিয়ে আর মার্থা আছে জেনেটিক্স এ। এরপরে ভিক্টর আর চন্দ্রা- দুজনেই রোবোটিক্স এ। ষষ্ঠ দম্পতি হলো রিচার্ড আর অরুণিমা- দু’জনেই মৌলকণার পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে। সপ্তম যুগল হলো বিজয় আর সুপর্ণা- দু’জনেই সেল বায়োলজিতে। অষ্টম দম্পতি মিলিন্দ আর সুনীতা- মাত্র কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়েছে ওদের- দু’জনেই নিউবায়োলজিস্ট।
নবম দম্পতি মার্ক আর বিপাশা- বয়সে সবচেয়ে কনিষ্ঠ এখানে, মাত্র ২০ আর ১৮ বছর বয়স ওদের, একমাস আগে বিয়েটা সেরে নিয়ে ওরা এখানে এসেছে, মার্ক পদার্থবিদ আর বিপাশা রসায়ণবিদ। সবার শেষে এসেছেন চার্লস আর এমি – দুজনেই মাইক্রোবায়োলজিস্ট।
তালিকা শেষ হলো এখানেই। এঁরা সারা জীবনের জন্য এখানে প্রবেশ করেছেন, এই প্রকল্প এক জীবনব্যাপী প্রকল্প, কারন এই এক্সপেরিমেন্টের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেখা যে মানবজীবন কিভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় এই Eco2 তে। আর মানুষের জীবন যেহেতু অন্য সব প্রানীর তুলনায় অনেক বেশী জটিল তাই পরীক্ষাটিও খুবই জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী।
এই দ্বিতীয় জীবমন্ডলে প্রথম মানবী-অতিথি, সুতনু আর সীবলীর মেয়ে সুকন্যা। প্রথম যখন ওর আসার সম্ভাবনার কথা শোনা গেল তখন যে কী সাংঘাতিক আনন্দ আর উত্তেজনা সকলের মধ্যে! ভিতরে যাঁরা রয়েছেন আর বাইরে যাঁরা রয়েছেন এই গবেষণায় তারা তো মহা উত্তেজিত। অভিনন্দনের বন্যায় প্রায় ছেয়ে গেল সুতণু আর সীবলীর চিঠির বাক্স, ফোনেও ঘন ঘন নানা অভিনন্দন-বার্তা। ওরা তো বলে পারেনা, আরে সব কিছু ঠিক্ঠাক চলতে দাও, এখনো অনেক দেরী, বাতাসে প্রাসাদ বানিও না – কিন্তু কে শোনে কার কথা।
যেদিন জন্মালো সুকন্যা, সেদিন ছিল ভালো একটা দিন, কি একটা পরবে সেদিন সবার ছুটি। কিন্তু ডঃ মহেন্দ্র ভৌমিক ছিলেন ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাজে অনেক দূরের এক দেশে, তাঁকে তো ফোনে এ বার্তা জানানো হলো, তিনি খুব তাড়াতাড়ি সফর সেরে দেশে ফিরে সেলিব্রেট করতে শুরু করলেন এই শুভ আবির্ভাব।। সত্যি, তাঁর আনন্দ একেবারে আন্তরিক, এই প্রোজেক্টই যে ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ডঃ ভৌমিক নিজে সুকন্যার নামকরণ করেছিলেন। এর প্রায় একবছর পরে দ্বিতীয় অতিথি এলো- এবারে একটি শিশুপুত্র, ঋতুপর্ণ আর মার্থার ছেলে আদিত্য। এবারেও নাম ডঃ মহেন্দ্র ভৌমিক নিজেই দিয়েছেন। এর পরে ক্রমে আরো অনেক নতুন নতুন ছেলেমেয়ে, দ্বিতীয় জীবমন্ডলের জীবন স্রোত বয়ে চলেছিল মসৃণগতিতে।
(২)
প্রথম ঝামেলা যেদিন দেখা দিল তা কেউ টেরও পায় নি। সেদিন ছিল সুকন্যার বারো বছরের জন্মদিন, কিশোরী সুকন্যা সত্যিই অত্যন্ত ঝকঝকে আর স্মার্ট, এরই মধ্যে স্নিগ্ধ সুন্দর অথচ দৃঢ় একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে ওর। সুতনু আর সীবলীর গোপন গর্ব ওকে নিয়ে।
সবাই মিলে সন্ধেবেলা ওকে নিয়ে উৎসব করলেন, সবাই নানারকম উপহার দিলেন ওকে। মুনলাইট পার্টি হচ্ছিল, তাই সেদিন সবাই নিজেদের ঘরের বাইরে। টলটলে চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাওয়া বাগানে সবাই যখন সুকন্যাকে নিয়ে উৎসব করছিল তখন, তখন তারা কেউই জানতো না সেদিন সকালেই সুকন্যা প্রথম প্রত্যুষের দেখা পেয়েছে।
প্রত্যুষ সুকন্যার থেকে ঠিক বছর চারেকের বড়ো। সেই কিশোর দারুণ বুদ্ধিমান ও সাহসী। নিয়ম ভাঙার ব্যপারে খুব ওস্তাদ, অবশ্য স্টেলার অফুরন্ত প্রশ্রয় এরজন্য খানিকটা দায়ী। প্রথম থেকেই সে অত্যন্ত স্মার্ট আর ছোটোবেলায় খুব দুষ্টু ছিল। কিন্তু স্টেলা ওকে কিছুতেই কড়াভাবে শাসন করতে পারতো না, কেবলই চোখ চলে যেত দেয়ালে টানানো সোফিয়ার হাসিমুখ ছবিটির দিকে, যেন ছবির ভিতর থেকে সেই মা চেয়ে দেখছেন কেউ তার প্রিয় সন্তানটিকে কিছু বলছে না তো?
একদিন খুব বেশী দুষ্টুমি করায় তো স্টেলা ডঃ ভৌমিককে বলে দিল। তখন বুঝতেও পারেনি কি করে বসেছে। সাত বছরের বাচ্চাটাকে ভদ্রলোক টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আধঘন্টা পরে তিনি বেরোলেন, আর স্টেলাকে তুলো ডেটল দিতে বললেন। স্টেলা ছুটে ঘরে ঢুকে দেখলো বাচ্চাটা মেঝেতে পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে, অনেক জায়গায় কেটে গেছে, রক্তে ভিজে গেছে।
স্টেলা প্রথমে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে বাচ্চাটা যখন স্টেলার দিকে চেয়ে রাঙা ঠোঁটে হাসলো, তখন মনে মনে স্টেলা প্রতিজ্ঞা করলেন আর কোনোদিন ওর নামে ওর বাবাকে কিছু বলবেন না।
সেদিন অবশ্য ওর বাবাও খুব আপসেট হয়ে গেছিলেন, সারারাত না ঘুমিয়ে জ্বরে আক্রান্ত ছেলের পাশে বসেছিলেন। শেষে স্টেলাই বলে কয়ে ওঁকে ঘুমোতে পাঠায়।
“স্টেলা, ও ভালো হয়ে যাবে তো? এতো জ্বর, আমি– আমি বুঝতে পারিনি, একটুও কাঁদে নি, চেঁচায় নি, আমি কি করে বুঝবো বলো যে এতো লেগেছে? যখন জামাটা লাল হয়ে গেল, তখন–তখন-”
“ঠিক আছে ঠিক আছে”, স্টেলা আশ্বস্ত করে, বলে, “জানি, আপনি বুঝতে পারেন নি, নইলে কেউ কি এরকম করে মারে নিজের ছেলেকে? বাচ্চা ছেলে, একটু দুষ্টুমী করেছে–তার জন্য এভাবে– আপনি ঘুমোতে যান। ও ভালো হয়ে যাবে। আমি তো আছি এখানে। আপনি মিছিমিছি রাত জাগবেন না স্যর, কালকে আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে।”
স্টেলার হয়েছে এখন যতো ঝামেলা, বাড়ীতে দুটোই তো ছেলেমানুষ – এ দুটোকে সামলে রাখা এক দায় হয়েছে ওর। যখন ইচ্ছে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে ও, কিন্তু কী যে মায়া পড়ে গেছে- আগে পড়েছিল বাচ্চাটার উপরে, এখন বাচ্চার বাবার উপরেও পড়ে গেছে। এত ধনী, এত জ্ঞানী,তবু সাংসারিক ব্যাপারে কিরকম অসহায়- কত রাতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে না খেয়েই বিছানায় লুটিয়ে পড়ে থাকেন ভদ্রলোক, স্টেলা ডেকে তুলে খেতে দেয়। তখন কিরকম করে যে কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকেন ভদ্রলোক, তা দেখে স্টেলার চোখে জল আসে। তাই ও জানে, ডঃভৌমিক মোটেই নিষ্ঠুর নন অত, যে বাচ্চাকে মেরে রক্তাক্ত করে দেবেন, কিন্তু হয়তো কোনো কারণে অস্থির ছিলেন আজ।
কিন্তু এরপর থেকে এক কান্ড হলো, প্রত্যুষ আর কোনোদিন ওঁকে বাবা বলে ডাকলো না। প্রথমে স্টেলা পর্যন্ত খেয়াল করে নি, ডঃভৌমিক তো বুঝতেই পারেন নি বহুদিন পর্যন্ত- প্রত্যুষ দরকার ছাড়া কথাই বলে না ওর বাবার সঙ্গে আর কথা বলার সময় শুধু দরকারী কথাটুকু বলে- সম্বোধনের দরকার হয় না। দিনে দিনে অনেক দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে বাবা আর ছেলের মধ্যে।
আজ ষোলো বছরের প্রত্যুষের জগৎ পুরোটাই আলাদা। ওর বন্ধুবান্ধব, বইপত্র, খেলাধূলা-এইসবের ঠাসা সূচীর ভিতরে ওর বাবা কোথাও নেই। স্টেলা আন্টি আছে–তবু কোথায় যেন তার সঙ্গেও একটা সূক্ষ্ম দূরত্ব আছে ওর। ওর সব বন্ধুরা- যারা ওকে প্রোটো বলে ডাকে, সকলের কাছেই খুব ভালো বন্ধু হওয়া সত্বেও কোথায় যেন প্রত্যুষ একা। সে কী সবসময় ওর সেরা হওয়ার জন্য? কোথায় যেন অন্যরা সাধারণ আর ও অসাধারণ।
ও বারো বছরেই ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র তৈরীতে দক্ষ হয়ে উঠছিল। বাবার টাকার অভাব নেই, ওর ছিল ছোট্টো একটা ল্যাব, সেখানেই সব বানাতো। ওর এসব দেখে কিন্তু ডঃ ভৌমিক দারুণ উৎসাহিত হতেন। ওকে উৎসাহ দিতেন। পড়াশোনাতে ও প্রথম থেকেই ভালো।এই ব্যাপারে ডঃ ভৌমিক কখনো হতাশ হন নি। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে ওকে গাইড করতেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে ও একদিন —
(৩)
আমরা আবার ফিরে আসি Eco2 তে, জন্মদিনের সন্ধ্যায় গোলাপী পোশাকে অপরূপা সুকন্যা। ছোটো ছোটো উপহার গুলো গুছিয়ে রাখছে। প্রজাপতির ছবিটা দেখতে দেখতে হাসি ফুটলো ওর মুখে। ছোট্টো শতদ্রুর অপটু হাতে আঁকা প্রজাপতি, জন্মদিনে সুকুদিদিকে ওর উপহার। এত সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাটা- দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে সুকন্যার।
তারপরে মনে পড়লো সকালের কথা-পাহাড়ের কাছে একটা ছোটো মাঠ- খুব সুন্দর সূর্যমুখী ফুল ফোটে ওখানে- খুব সকালে সুকন্যা ওখানে ঘুরছিল আর একটা সূর্যমুখী তুলে চুলে গুঁজেছিল। কেন যে বেশ কিছুদিন হলো ওর খুব একা একা ঘুরতে ইচ্ছে করে কেজানে। খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে সে, শরীরে ও মনে। বড়ো হয়ে উঠছে তাড়াতাড়ি— অনেক নতুন কিছু ঘটছে ওর নিজের মধ্যে আর বদলে যাচ্ছে ওর পৃথিবীকে দেখার চোখ।
প্রথম যেদিন সে ঋতুমতী হলো- তার আগেই অবশ্য মা ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন তাকে–কিন্তু সেই জানা আর নিজের অভিজ্ঞতায় জানা কতই না আলাদা। আগে থেকে জানা সত্বেও অদ্ভুত এক আশংকা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, অজানা ভয়ে কেঁদে ফেললো সে।
মা খুব আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “দূর বোকা মেয়ে, এতে ভয়ের কি আছে? এ আমারও হয়, আমার মায়েরও হতো। সব মেয়েরই হয়।” মা খুব ভালো সুকন্যার, চারিপাশে সবাইই খুব ভালো। তবু যে কেন সুকন্যার মন উতলা হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে সে জানেনা। খুব ছটফট করতে থাকে মনের খুব ভেতরটা। নিজের ঘরে একেবারে একলা হয়ে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে – অনেক দূরের কোনো দেশের কথা। সেখানকার মানুষদের কথা। অজানা অচেনা সব মুখ এসে ওর স্বপ্নমগ্ন চেতনায় ধরা দেয়। অথবা একলা একলা ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে নদীর ধারে, বনের কাছে, বড়ো বড়ো ছায়াঘন গাছের নীচে– রোদ্দুর ভরা মাঠে, সোনালী বালুচরে—-
এখানে যারা আছে তারা যে সবাই বড্ড চেনা, বড্ডো ছকে বাঁধা। বড়োরা সবাই এত ব্যস্ত সর্বদাই আর ছোটোরা যে সবাই ওর থেকে ছোটো। সুকন্যা মানসিক দিক থেকে অনেক বেশী পরিণত। শুধু পড়াশুনো, বই, স্কুল, কম্পিউটার, মুভি – এইসব, যা নিয়ে এতকাল ব্যস্ত ছিল সে তা হঠাৎ কেমন যেন একঘেয়ে ঠেকছে তার কাছে। একলা ঘরে আয়নার সামনে সে নিজেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, অজানা ভালোলাগায় মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তারই সঙ্গে আবার কোথায় যেন একটা সুদূর বেদনা। সুকন্যা জানতো না পৃথিবীর সব মেয়েরাই বয়ঃসন্ধিতে প্রায় একই রকমের ভাবনার আচ্ছন্ন হয়।
সুতনু আর সীবলী নিজেদের গবেষণায় খুবই ব্যস্ত। আলাদা করে আর মেয়ের দিকে বিশেষ নজর রাখার কথা ওদের মনে হয় নি। সুকন্যা পড়াশোনায় এত ভালো, ব্যবহারেও নিখুঁত, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বও শাণিত হয়ে উঠছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে- তাই ওঁরা নিশ্চিন্ত ছিল।
সেই জন্মদিনের সকালে- সেদিন রবিবার, তাই ছুটি, সুকন্যা ঘুরছিল সূর্যমুখীর মাঠে, কেউ ছিল না কাছে পিঠে- অনেক দূরে ধানক্ষেতে একটা রোবোট নীচু হয়ে ধান কাটছে – দূর থেকে শুধু তার পিঠটা দেখা যাচ্ছে।
পাহাড়ের খুব কাছে চলে গিয়েছিল সুকন্যা – হঠাৎ সে চমকে গেল এক নতুন কিশোরকে দেখে। হাল্কা নীল রঙের শার্ট পরা আর ঘননীল রঙের ট্রাউজার্স, মাথার সোনালী চুলগুলো এলোমেলো আর বাদামী উজ্জ্বল চোখে আশ্চর্য দুষ্টুমীর হাসি। এখানের সবাইকে তো চেনে সুকন্যা-কিন্তু এ কোথা থেকে এলো? এখানে তো বাইরের কারুর আসার অনুমতি নেই!
ছেলেটাই প্রথম হেসে হাত বাড়ালো, বললো, “গুড মর্নিং। আমি প্রত্যুষ। আপনার নাম?”
সুকন্যা হেসে ফেললো, “আমাকে কেউ এখানে আপনি বলে না। এসো আমরাও তুমি বলি। বলবে?”
প্রত্যুষ এই আশ্চর্য কিশোরীর অপূর্ব সারল্যে আর স্মার্টনেসে এক মুহূর্তের মধ্যেই মুগ্ধ হয়ে গেল। সে যেখানে পড়াশোনা করে সেখানের বন্ধুরা সবাই চেনা, সবাই বড্ডো ছকেবাঁধা। ওদের চলা বলায় বড়ো বেশী ভনিতা। প্রত্যুষের অসহ্য লাগে।
প্রত্যুষ হেসে মাথা কাত করলো, বললো, “হ্যাঁ, তাই ভালো। আমার আপনি শুনতেও ভালো লাগে না, বলতেও না। কিন্তু তোমার নামটা তো বললে না!”
সুকন্যা হেসে বলে,” আমার নাম সুকন্যা। তোমার নামটা কিন্তু ভারী সুন্দর। প্রত্যুষ মানে সকাল না? এখন সকাল বেলা, আর তুমি ঠিক এখনই এসেছ।”
“বাবাঃ, তুমি তো দেখছি কঠিন কঠিন শব্দের মানেও জানো।”
“কিন্তু প্রত্যুষ, তুমি এখানে এলে কি করে? এখানে তো বাইরে থেকে কারুর আসার অনুমতি নেই!”
“তা নেই বটে, তবে প্রত্যুষের অনুমতি না হলেও চলে।”
দুষ্টুমীর হাসিটা এবার আরো উজ্জ্বল ওর চোখে- বললো, “চলো সুকন্যা, ওখানে নদীর ধারটায় বসে তোমাকে বলি আমার লুকোচুরি খেলার কথা।”
নদীর ধারে পৌঁছে দুজনে বসলো একটা চ্যাটালো পাথরের উপরে। পাথরটা অনেকটা ঝুঁকে আছে নদীটার উপরে। নদীর জল কাঁচের মতো স্বচ্ছ, নীচে চিকচিক করছে বালি। স্রোত এসে অল্প অল্প ধাক্কা দিচ্ছে পাথরটার গায়ে, ফেনিয়ে উঠছে জল। এই জায়গাটাও ভারী প্রিয় সুকন্যার।

প্রত্যুষ যাদুকরের মতো পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনলো একটা ক্ষুদে যন্ত্র। বললো, “বলো তো এটা কী?”
ক্ষুদে একখানা জিনিস, চারকোনা, মধ্যে একটা ছোট্টো জায়গায় লাল নীল আলো জ্বলছে আর নিভছে। সুকন্যা অবাক হয়ে গেল। বললো, “কী এটা?”
“এটা হলো বড়োদের বোকা বানাবার যন্ত্র। ওরা তো সবসময় ভাবে যে ওরা সবই জানে, কিন্তু ওরা জানেনা যে প্রত্যুষের আবিষ্কারের কাছে সবসময় বড়োগিরি চলে না।”
“তুমি দেখছি বড়োদের উপর খুব চটা। কিন্তু আমাকে আরো একটু ভালো করে বুঝিয়ে দাও এটা আসলে ঠিক কী।”
“এটা একটা ডি-বাগিং মেশিন। এটা চালু থাকলে কিছুতেই ওদের নেটওয়ার্ক আর আমায় লোকেট করতে পারে না, আমার কাছাকাছি যারা থাকে তাদেরও নয়। আসলে ওরা সবসময়ে এই Eco-2 এর ভিতরে কে কোথায় আছে ঠিক দেখতে পায়-খুব ভালো অডিও-ভিডিও নেটওয়ার্ক– সব সময়ে তোমরা রয়েছ ওদের নজরদারিতে। তোমরা কখন কোথায় যাচ্ছ আর কী করছো আর কী বলছো সব চলে যাচ্ছে ওদের কাছে। কিন্তু যদি আমার এই ডি-বাগিং মেশিনটা তোমার কাছে থাকে আর এটা চালু থাকে তাহলে ওরা আর তোমার খোঁজ পাবে না।” বলতে বলতে প্রত্যুষের চোখ উজ্বল হয়ে জ্বলছে।
সুকন্যা হাসে বলে, “তাহলে এখন তুমি আর আমি দু’জনেই মুছে গেছি ওদের নেটোয়ার্ক থেকে?
“হ্যাঁ, দু’জনেই। কিন্তু তোমার পক্ষে খুব বেশীক্ষণ এভাবে থাকাটা উচিত হবে না প্রথমদিনই। আমি অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই এখানে আসি। তোমাকে দেখেওছি দূর থেকে, কিন্তু দেখা করি নি।”
“কেন দেখা করো নি? লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা কি ভালো?”
এই সরল কিশোরীর সচ্ছন্দ প্রশ্নে হঠাৎ কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে প্রত্যুষের মতো স্মার্ট ছেলেও। কোনোরকমে সামাল দিতে বলে, “আসলে তোমাকে বিরক্ত করতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে নি। তুমি আপনমনে ঘুরছিলে, মাঠের ঘাসফুল তুলছিলে, দূর থেকে দেখতেই ভালো লাগছিল আমার।”
সুকন্যা বুঝতেও পারলো না ওর ফুটফুটে ফর্সা গালে হঠাৎ লালচে ভাব দেখা দিল। দেখে প্রত্যুষের কেন যে ভালো লাগলো কে জানে।
সুকন্যা বললো “তুমি যে এখানে ঢুকেছ তা যদি ওরা জেনে ফেলে?”
“তাহলে কী হবে? কী আর হবে- প্রত্যুষকে ওরা ঐ উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে এক ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেবে।” প্রত্যুষ বেশ গম্ভীরভাবে ঠাট্টা করতে পারে।
কিন্তু সুকন্যার মুখ হঠাৎ সাদা হয়ে যেতে দেখে ও ঘাবড়ে যায়- বলে, “আরে, তোমার মুখ শুকিয়ে গেল যে একেবারে। তুমি ভারী বোকা মেয়ে, ঠাট্টা বোঝ না?”
সুকন্যার মুখ সত্যিই শুকিয়ে গেছিল, প্রত্যুষকে হাসতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। বললো, “এইরকম ঠাট্টা আর যেন কখনো কোরো না।”
প্রত্যুষ আরো কিছুক্ষণ গল্প করে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। ঐ গিরিপথের বাঁকে মিলিয়ে গিয়েছিল ওর চলন্ত অবয়ব। আর সুকন্যা ফিরে এসেছিল ঘরে- চুলে গোঁজা সূর্যমুখী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে।
এখন রাতের বেলা – এই ঘর সুকন্যার একলার-বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ভাবছে কোনোদিন যদি ও প্রত্যুষকে বলে ওকে বাইরে নিয়ে যেতে?
ভাবামাত্রই শিউরে ওঠে সুকন্যা- সে জানে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর যদি কোনোদিন প্রত্যুষ ওকে নিয়ে যেতে চায়?
পাশের ঘরে সুতনু আর সীবলী অঘোরে ঘুমোচ্ছে, সারাদিনের পরিশ্রমের পরে ওরা প্রত্যেকদিনই খুব ক্লান্ত থাকে। সুকন্যা তাদের একমাত্র সন্তান। সুতনু আর সীবলী আরও একটি সন্তান চেয়েছিল -কিন্তু নানাকারণে সেই চাওয়া সফল হয় নি – আসল কারণ কি সেটাই, নাকি ওরাও নিজের অজান্তে জড়িয়ে গেছে কোনো জালে? ওদের জীবনও কি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বাইরে থেকে?
পাশের ঘরে মাবাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে-কিন্তু সুকন্যার চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না কেন আজকে? বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় সে উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে।
দরজা খুলে বারান্দা পার হয়ে বাইরে এলো- আকাশে চাঁদ নেই, ফুটফুট করছে এক আকাশ তারা। সে বসে পড়লো ঘাসের উপরে, তারপরে লুটিয়ে শুয়ে পড়লো নরম ঘাসে। ঘাড়ের কাছে ঘাসের সুড়সুড়িতে ভারী আরাম লাগছে সুকন্যার। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশটা দেখতে দেখতে অদ্ভুৎ ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে সে। অনেকগুলো তারার নাম সে জানে, জানে অনেকগুলো নক্ষত্রমন্ডলের নাম। ঐ তো বৃশ্চিকরাশি, তার মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে কমলা রঙের জ্যেষ্ঠা। ঐ তো ধনুরাশি, ঐ উত্তরে রাজহংসমন্ডল। আর হাল্কা ওড়নার মতন উত্তর থেকে দক্ষিনে ছড়ানো ঐ তো ছায়াপথ।
তারাগুলোকে দেখতে দেখতে ওর ক্লান্ত চোখ ভরে ঘুম নেমে এলো। ঘুমের মধ্যে আশ্চর্য সব স্বপ্ন-তারপরে নিথর হয়ে গেল ও, শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিল। রাতের বাতাস ওর রেশমী চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করছিল। বাতাসে রাত্রির ফুলের সৌরভ, ও জানতে পারছিল না।
তখন শেষরাত অথবা প্রথম ভোর- হঠাৎ কাঁপুনি ধরলো ওর, জেগে উঠে সুকন্যা দেখলো সে বাইরে শুয়ে ঘুমিয়ে গেছিল। উঠে বসলো সে, আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো তারারা ম্লান হয়ে গেছে, শুধু পুব অকাশে দপদপ করে জ্বলছে শুকতারা। ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়া ওড়নাটা তুলে নিল ও, শিশিরে ভিজে গেছে সেটা। ঘরে গিয়ে এবার দরজা বন্ধ করে নিজের বিছানায় শোয় ও। চোখ বন্ধ করে ও দেখতে পেল প্রত্যুষকে, ওর হাসি, ওর গিরিপথের বাঁকে মিলিয়ে যাওয়া অবয়ব। সুকন্যা ভাবে, কাউকে তো একথা বলতেও ও পারবে না কোনোদিন। তাহলে প্রত্যুষ ধরা পড়ে যাবে। আর হয়তো খুব কঠোর শাস্তি পাবে।
পরদিন থেকে সবই ঠিকঠাক চলছিল, শুধু সুকন্যার শিক্ষক-কম্পিটার ওর একটা অংকে মারাত্মক একটা ভুল পেলো। এইরকম ধরনের ছোটো অথচ মারাত্মক ভুল ওর কোনোদিন হয় না বলে যন্ত্রটি চিন্তিত হয়ে পড়লো।
দুপুরে সুকন্যা লাঞ্চ করতে গেল। সেসময় কম্পুটিচার ওর মায়ের কম্পুটারে সংকেত পাঠালো। সীবলী এসে সব শুনে কিন্তু তেমন খুব একটা বিচলিত হলো না। মানুষের তো সময়ে অসময়ে ভুল হয়ই, তাই নয় কি?
কম্পুটিচার বারে বারে বললো, এইরকম ভুল কোনোদিন হয় নি সুকন্যার, তাই সে খুব অবাক হয়েছে।
পর পর তিনবার ভুল হলে ছোট্টো করে শাস্তিমূলক শক দেবার কথা। একবার হয়ে গেল, আরো যদি দু’বার হয়, তাহলে সত্যি সত্যি ঐ মিষ্টি নরম মেয়েটাকে শক দিতে হবে নাকি? এই চিন্তাতেই কম্পুটিচার মুষড়ে যেতে থাকলো।
দু’দিন পরে, সুকন্যা অনুভব করলো কোথায় একটা গন্ডগোল হচ্ছে। সে সেদিনের পর আর ভুল করে নি বটে, কিন্তু প্রত্যেকদিন সকালে কাজ শুরুর সময় কম্পুটিচার কেমন যেন কাঁপা গলায় মনে করিয়ে দিয়েছে, আজকে ভুল করবে না তো, সুকন্যা?
একদিন ও জিজ্ঞেস করে বসলো, “তোমার কী হয়েছে কম্পু? তুমি আগে পড়া হয়ে গেলে কতো হাসির গল্প বলতে, কতো সব ভালো ভালো ছবি দেখাতে। ক’দিন ধরে তো কই সেরকম করছো না? তুমি আমার উপরে রাগ করেছ, কম্পু?”
কম্পু কিছু বলে না, চুপ করে থাকে।
পরের দিন সুকন্যা ইচ্ছে করে দু’টো ভুল করলো। কম্পুটারের মনিটরটা টকটকে লাল হয়ে গেল। দু’টো বিরাট দাঁড়া বেরিয়ে এলো পিছন থেকে। সুকন্যা পালাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু পারলো না। একটা ঝিম ধরানো রশ্মি ওকে অবশ করে দিল।
শক খাবার পরে সুকন্যা যখন মাটি থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে, মনিটর তখন ধূসর, একটা অস্পষ্ট কান্না শোনা যাচ্ছিল। সুকন্যা অবাক হয়, সে নিজে তো ঠিকই আছে, তেমন লাগেও নি ওর। শুধু একটা ঝাঁকুনির কথা অনুভবে আসে, তারপরেই একমুহূর্তের জন্য সব অন্ধকার হয়ে গেছিল।
তাহলে কে কাঁদছে, নাকি মনের ভুল? সুকন্যা নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, পেলে দেখতে পেতো মুখটা অসম্ভব ফ্যাকাশে। সে যে ঠিকমতো হাঁটতেও পারছে না, অল্প অল্প টলছে, সেটাও সুকন্যার খেয়াল হলো বেশ কিছুক্ষণ পরে।
এরপর দিন থেকে, সুকন্যা শুরু করলো এক কান্ড। প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা, ছুটি হবার ঠিক আগে সে ঠিক গুণে গুণে তিনটে ভুল করে। কম্পুটিচার প্রত্যেকদিন ওকে শক দিতে বাধ্য হয়। প্রত্যেকদিন শক খেয়ে সুকন্যা টলতে টলতে চলে যায়, কম্পু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এটা যে সুকন্যার একটা খেলায় পরিণত হয়েছে, সে বোঝে না।
একদিন সুকন্যার খুব জ্বর ছিল, বলে নি কাউকে। জ্বর গায়ে শক খাবার পরে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। ক’দিন এখন ওর পড়ায় ছুটি। কম্পুর কাছে ক’দিন আসে না। ওর মা সীবলী হঠাৎ বুঝতে পারলেন কোথাও একটা কিছু গন্ডগোল হয়েছে। সুকন্যা আর ঠিক আগের মতন নেই। বেশ বদলে গেছে। আগে ও মায়ের কাছে সব কিছু দিব্যি বলতো, এখন বলে না। সীবলী জানে এই কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ বড়ো স্পর্শকাতর সময়। এইসময় খুব সাবধানে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। জোরাজুরি করতে গেলে হিতে বিপরীত হবারই বেশী সম্ভাবনা।
জ্বরে আক্রান্ত সুকন্যা বিছানায় শুয়ে আছে-ওর মা সীবলী ওর শিয়রের কাছে বসে ওর কপালে হাত বোলাচ্ছেন। সীবলী এ কদিনের জন্য কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন, অবশ্যই ডঃ ভৌমিকের গবেষকদলের অনুমতি পাবার পর।
সুকন্যার কপালে আলতো হাত বোলাতে বোলাতে খুব নরম সুরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “মামণি, তোর এখন একটু ভালো লাগছে?”
“লাগছে মা, খুব ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি যে আজ বাড়ীতে রইলে, তোমার কাজের ক্ষতি হবে না তো?”
“না, আজকে ছুটি নিয়েছি। কত ছুটিই তো জমে গেছে। তাই ভাবলাম আজকে–”
“আমার তো বেশী জ্বর নয়। খালি একটু মাথাব্যথা। তুমি এর জন্য কেন এতো ভাবছো?”
“আমার যখন ছোটোবেলা জ্বর হতো, মা তখন খুব সেবাযত্ন করতো। এমনিতেও সবসময়েই খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করতো। মা তো চাকরি করতো না। আমি তো তোকে তেমন ভাবে দেখাশোনা করতে পারি না। মামণি, এর জন্য তোর মনে কোনো দুঃখ নেই তো? তোর বেশী একা একা লাগে না তো?”
“না মা, একা একা কেন লাগবে? আমার পড়া আছে, কম্পু আছে, কতরকমের খেলা আছে, মুভি আছে–আরও কত কী আছে। তুমি আমার জন্য ভেবো না।”
সুকন্যার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে কেন কে জানে সীবলীর দু’চোখ ভরে জল এলো।
সুকন্যা মায়ের চোখের জল নিজের দুহাত দিয়ে মোছাতে মোছাতে বললো, “বোকা মেয়ে তুমি। কাঁদছো কেন শুধু শুধু?”
তারপরে খুব নরম গলায় সীবলীকে জিজ্ঞেস করলো, “মা তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো?”
“কী প্রশ্ন রে?”
“মা, আমার কোনো ভাই বা বোন তোমরা আনলে না কেন? এখানে তো প্রায় সবারই দুটো বা তিনটে ছেলেমেয়ে। তোমাদের শুধু তা নয়।”
সীবলীর মুখ কেন জানি ম্লান হয়ে গেল। খুব আস্তে আস্তে বললো, “আমরা তো রাজীই ছিলাম, হলো না, কী করবো বল। তোর কি খুব একা লাগে?”
“না না, তা নয়। তবে মাঝে মাঝে ভাবি একটা দুষ্টুমিষ্টি বোন থাকলে কেমন হতো। তুমি কি কিছু মনে করছো তোমাকে এইসব জিজ্ঞেস করছি বলে?”
সীবলী ভাঙা গলায় বললো, “আমিও চেয়েছিলাম একটা ফুটফুটে ছেলে। তোর একটা মিষ্টি ভাই। কিন্তু আমার ইউটেরাসে ইনফেকশান হলো। ওটা অপারেশন করে বাদ দিতে হলো। তবু কাউকে সারোগেট হিসেবে নিয়ে আমরা পেতেই পারতাম আমাদের দ্বিতীয় সন্তান। মার্থা, সুপর্ণা- সবাই উৎসাহী ছিল সারোগেট মাদার হতে। এখানকার ক্লিনিকে ইন ভিট্রো এর সব কিছু সুবিধেই আছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ডঃ ভৌমিক অনুমতি দিলেন না। বললেন এতে নাকি নিজেদের মধ্যে সমঝোতা কমে যাবে আমাদের।”
সীবলী অঝোরে কাঁদছিল। এবারে সুকন্যা ওর মায়ের মুখ নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্বান্তনা দিতে থাকে। বলে, “বিশ্বাস করো মা, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই নি। আমি এসব কিছু জানতাম না। তুমি মিছিমিছি আর কষ্ট পেয়ো না।”
সীবলী চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হেসে মেয়েকে নিবিড় করে ধরে কপালে চুমো খায়। বলে, “আমার সুকুকে তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।”
কেন কে জানে সুকন্যার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে অজানা আশংকায়। মা তো প্রত্যুষের কথা জানেনা। কোনোদিন মাকে তো বলতেও পারবে না সুকন্যা। অথচ মা তাকে কত বিশ্বাস করেন। আত্মগ্লানি হয় সুকন্যার। ঠোঁট কাঁপে, চোখ ভরে উঠতে চায় জলে।
কেন এইরকম হলো? এতদিনের সহজ সরল সম্পর্ক কেন আর তেমন রইলো না?
সুকন্যা জানতো না এই ক্ষুদ্র পৃথিবী পেরিয়ে ঐ যে বিরাট পৃথিবী-তাও পেরিয়ে যে বিরাট আকাশ-সে আকাশভরা কত লক্ষ লক্ষ তারা-দূর দূরান্তে ছড়ানো কত কোটি কোটি গ্যালাক্সি-অফুরান মহাবিশ্ব- সেই মহাবিশ্বের অমোঘ নিয়মে পরিচালিত তারা। সে, তার মা, বাবা, এখানকার সবাই আর এখানকার নিয়ন্ত্রক ঐ তারাও। ডঃ ভৌমিক কি করে সেই সর্বব্যপ্ত ইচ্ছাকে বাধা দেবেন? নিজেদের ছোটো ছোটো বানানো নিয়ম দিয়ে মানুষ নিজেদের বাঁধতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে যে নিজেকেই চোখ ঠারা।
লাইব্রেরীতে খুঁজতে খুঁজতে একদিন এক ছুটির দুপুরে সুকন্যা পেয়ে গিয়েছিল একটা আশ্চর্য গল্পের বই। অনেককাল আগের এক সাংবাদিক-লেখকের কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি। বইটার নাম “ভবিষ্যতের অতীত”। কি অদ্ভুত এক আবদ্ধ সমাজের কথা ছিল সেখানে। যন্ত্রপাতিতে খুব উন্নত তারা। কিন্তু কোনো স্বাধীনতা নেই কারুর।
মায়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে এলিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে সুকন্যার কেন যে ঐ বইটার কথা মনে হলো কে জানে। তাহলে কি এখানেও তারা ঐরকমই বন্ধনে বন্দী? একদল পরপরিচালিত রোবোট মাত্র তারা? অন্যের ইচ্ছার ক্রীতদাস?
পরদিন জ্বর সেরে গেল সুকন্যার। এবার কম্পুটিচারের কাছে গেল। পড়াশুনো করলো। কিন্তু পড়া শেষ হলে আজ আর গল্প খুললো না, ছবি আঁকলো না। ক্লাস শেষ হয়ে যাবার মুখে আজ আর ভুল করলো না ইচ্ছে করে। কম্পু অবাক হয়ে রইলো।
উদাসীন মুখে সুকন্যা ফিরে গেল নিজের ঘরে। বিছানায় এলিয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতে থাকলো। কিন্তু ভালো লাগলো না বেশীক্ষণ। একসময় উঠে কফি তৈরী করে খেল।
বাবা-মার ফিরতে অনেক দেরী। রাতে ল্যাবে কাজ থাকলে ফিরতে নাও পারে। ওখানেই কফি স্যান্ডউইচ খেয়ে নেবে। এরকম কতদিন হয়েছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত ওরা ফেরেনি।
যাক, তাতে সুকন্যার বয়েই গেল। সে নিজে একা একা থাকতেই বেশী পছন্দ করছে আজকাল। এখনো বেশ আলো আছে বাইরে। মিষ্টি বিকেল।
সুকন্যা বেরিয়ে ওর সেই প্রিয় সূর্যমুখীর মাঠের দিকে চলতে শুরু করলো। অল্প অল্প হাওয়া ওর কপালের কাছের অবিন্যস্ত চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করছিল। আচ্ছা, প্রত্যুষ কী করছে এখন? লেকের ধারে হাওয়া খাচ্ছে? নাকি ওর সেই বান্ধবী জুলিয়াকে নিয়ে ঘুরছে?
জুলিয়ার কথা প্রত্যুষই বলেছিল একদিন। বলেছিল ভালো বন্ধু ওরা। কিন্তু তবু সুকন্যার বুকের মধ্যেটায় চিমটি কাটার মতো ব্যথা করছে কেন? যাকগে মরুকগে ওসব কথা আর ভাববে না সুকন্যা। প্রত্যুষই বা ওর কে এমন যে ওর কথা এত করে ভাবতে যাবে সুকন্যা?
সুকন্যা এখানে একাই একেশ্বরী– কোথাকার কে প্রত্যুষ এসে ওর জগৎটা ওলোটপালোট করতে চাইলে ও তা দেবে কেন? আর ও ছেলেটা তো নিয়ম ভেঙে এখানে ঢোকে, ও তো অপরাধী, অন্যায়কারী!
সুকন্যা ভাবতে ভাবতে ঠোঁট কামড়ায়। ওর কি বলে দেওয়া উচিত যে প্রত্যুষ এখানে এভাবে ঢোকে? না বলে কি সে নিজেও অপরাধ করছে? কিন্তু বললে যে ও ধরা পড়ে যাবে! কি জানি কী করবে বাইরের ওরা ওকে। পড়ুক না ধরা, পাক না সাজা- সুকন্যার মনের ভিতরে একটা অংশ একথা বলছে, আরেকটি অংশ কিছুই বলছে না, নিঃশব্দ অশ্রুতে সিক্ত হয়ে যাচ্ছে।
কী দায় পড়েছে ওর? যে যা খুশী করুক, ওর তাতে কী? ওর উপরে কি কেউ দায়িত্ব দিয়েছে সবার কাজ ঠিক করে দেওয়ার?
কি জানি কী হলো-বসন্তের কচি ঘাস আর অজস্র ঘাসফুলে ভরা সেই মাঠে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকলো সুকন্যা। ওর মন বলতে লাগলো, “এসো এসো তুমি, আমার মন কেমন করছে। খুব মন কেমন করছে।”
কেন যে ওর মনে হচ্ছে কেউ নেই ওর! কোথায় এক অজানা দেশে হারিয়ে গেছে ও। মা নেই, বাবা নেই, চেনা জানা কেউ নেই। কেউ আসতেও পারবে না। একমাত্র সেই নিয়ম ভাঙা কিশোর কেবল আসতে পারে, সে যে বাধা মানে না!
“এসো, এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও আমায়। আমি হারিয়ে গেছি। আমি হারিয়ে গেছি।”
(৪)
অনেক দূরে, প্রত্যুষ নিজের ঘরে একটা জটিল ধাঁধার উত্তর বার করার চেষ্টা করছিল। হঠাত ফোন বেজে উঠলো। উঃ, এই এক যন্ত্রণা। কিছুতেই কোনোকিছুতে মন দিতে দেবে না। এই জন্য সেলফোন ভালোবাসে না প্রত্যুষ। কিন্তু উপায় কী? কেউ কথা বলতে চাইছে, জরুরী কিছু হতে পারে, ফোন না তুলে কী করবে?
ভাবতে ভাবতে কথাবোতাম অন করে কানে ফোন তুলেছে। “হ্যালো, প্রত্যুষ স্পিকিং।”
“প্রোটো, আমি জুলিয়া বলছি। এই বিকেলে ঘরে বসে বসে কী করছো? লেকের ওখানে আসবে? “
প্রত্যুষ দাঁতে দাঁত চাপলো। কেন এরকম সময়ে অসময়ে লোকে বিরক্ত করে? কিছু বলাও যায় না কড়া করে, ভাববে প্রত্যুষ অসামাজিক। তবু বলতে পারতো, কিন্তু এই জুলিয়াকে যে বাবা খুব পছন্দ করেন! ভেবেই রেখেছেন যথাসময়ে ওকেই পুত্রবধূ করবেন।
কিন্তু প্রত্যুষের যে একটুও মত নেই একথা কে বোঝায়! আগে আগে ওরও যে জুলিয়াকে ভালো লাগতো না, তা নয়। বেশ কবার ওর সঙ্গে বেড়াতেও গিয়েছে সে। কিন্তু মেয়েটা এত কৃত্রিম!
বাবাকে বলতে গেলে তো কুরুক্ষেত্র ঘটে যাবে। উনি নিজে সবসময় কতৃত্ব করতে পছন্দ করেন। নিজের ইচ্ছাই ওঁর কাছে শেষ কথা, অন্য কারুর যে অন্য রকম ভাবনা থাকতে পারে- তা যেন কিছুতেই উনি মানতে পারেন না!
গলার স্বরে বেশ খানিকটা মধু মিশিয়ে জুলিয়ার প্রোটো বললো, “জুলি, ডার্লিং, আমি আজকে যে বড্ড ব্যস্ত! আগামীকাল যাবোই। কথা দিচ্ছি।”
“সব সময় তুমি ব্যস্ত। আমার ভালো লাগে না। কী করছো আজকে?”
“ইলেকট্রনিক্স এর একটা মডেল। প্রায় হয়ে গেছে। আজকে রাতে বাবা দেখবেন ওটা চালিয়ে। তার আগে শেষ করতেই হবে ডার্লিং।”
বাবা শুনেই জোঁকের মুখে নুন পড়লো। জুলিয়া নরম গলায় বললো, “ও, উনি দেখবেন? ঠিক আছে। তুমি খুব মন দিয়ে কাজ করো। যেন ভালো বলেন।”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, মন দিয়েই তো করবো। রাখি?”
ফোন রেখে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলো প্রত্যূষ। ধাঁধার উত্তরটা প্রায় ধরে ফেলেছিল। কিন্তু মোক্ষম সময়ে মেয়েটা— এখন সব গেছে গুলিয়ে। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। মুখের ভেতরটা তেতো লাগছিল ওর।
ঘর থেকে গেল ল্যাবে। সত্যিই বাবা আজকে রাতে ওর ইলেকট্রনিক্স এর নতুন মডেলটা দেখবেন। হয়ে গেছে আগেরদিনই। ওটার গায়ে আলতো হাত বোলালো প্রত্যুষ। আস্তে করে বললো, “আমায় ডুবিও না বাবা মডেল। জানো তো বাবা দক্ষযজ্ঞ বাঁধাতে সব সময় তৈরী হয়েই থাকে।” বলে হাসলো, কিন্তু হাসিতে তিক্ততা লেগে রইলো নিমপাতার মতো।
অজান্তে ওর হাত চলে যায় চিবুকের উপরে, সেখানে বহুকাল আগের একটা দাগ। ক্ষত শুকিয়ে গেছে কবেই, শুধু দাগটা আছে। সাদা সুডৌল চিবুকের উপরে ছোটো অথচ উগ্র একটা বাদামী দাগ। কেন যে বাবার সামনে গেলেই এটাতে ব্যথা করে কে জানে। কোনো কারণ নেই, এতকাল পরে এখানে ব্যথা না হবারই কথা, কিন্তু তবুও বড্ড ব্যথা করে।
বাবাকে কোনোদিন বলতেও তো পারবে না, “বাবা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি সামনে আছো বলে, খুব ব্যথা করছে।”
ইশ, এরকম বললে ভদ্রলোক কিরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যে যাবেন! ডঃ ভৌমিকের সেই মুখ কল্পনা করেই ফিক করে হেসে ফেললো প্রত্যুষ। এবারের হাসিতে আর নিমপাতা গুঁড়ো লেগে রইলো না। গুঁড়ো আবীরের মতো রঙ ছড়িয়ে গেল সবটা জুড়ে।
প্রত্যুষ ভাবলো আগামীকালই একবার দেখা করতে যেতে হবে সুকন্যার সঙ্গে। সুকন্যার নামটা মনে পড়তেই মনটা ভারী প্রসন্ন হয়ে উঠলো ওর।
সন্ধেবেলা ডঃ ভৌমিক দেখতে এলেন ছেলের তৈরী মডেল। দেখাতে দেখাতে সব ভালো করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলছিল প্রত্যুষ। মাঝে মাঝে ওকে থামিয়ে প্রশ্ন করেন বাবা, ও যথাযথ উত্তর দিয়ে ভদ্রলোককে খুশী করে দেয়। সব দেখানো হলে এবার যন্ত্রটা চালালো ও। খুব ভালোরকমই চললো। ডঃ ভৌমিক এত খোলাভাবে প্রশংসা করতে লাগলেন যে তিনি নিজেই অবাক।
সব কিছু শেষ হলে প্রত্যুষ বললো, “আমাকে আগামীকাল ছুটি দেবেন? আমি একা একা পাহাড়ে যাবো ভাবছিলাম ট্রেকিং করতে। অনেক দিন কোনো ব্রেক নেওয়া হয় নি। বড্ড ক্লান্ত। দেবেন?”
প্রত্যুষের গলা সত্যিই ক্লান্ত শোনাচ্ছিল। আসলে ওর চিবুকের দাগটায় খুব ব্যথা করছিল।
ডঃ ভৌমিক ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলেন। গম্ভীর আর বিষন্ন। এই যে এত ভালো বললেন, তার কিছুই ওকে ছোঁয়নি। তাহলে কি কোথাও ভুল হচ্ছে? বাবা বলে ডাকে না কেন ছেলেটা? সেই কবেকার ভুল ক্ষমা করতে পারেনি?
হাত দিয়ে চিবুকটা ঘষছে কিরকম অস্থির হয়ে। ডঃ ভৌমিক তাড়াতাড়ি বললেন, “ঠিক আছে ঠিক আছে, এতে আর অসুবিধে কী আছে? কালকে তোর ছুটি। ব্রেক। তোর যেখানে খুশী যাস।”
একথা শুনে হাসি ফুটলো ওর মুখে, ম্লান বিষন্ন হাসি। তারপরে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। ডঃ ভৌমিক খুব চিন্তিতভাবে নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন।
পরেরদিন খুব ভোরবেলাতেই প্রত্যুষ উঠে ট্রেকিং এর পোশাকে তৈরী হয়ে নিল। সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে স্টেলা আন্টির কাছে বিদায় নিয়ে যখন বেরিয়ে গেল তখনো সূর্য ওঠে নি। ঊষার গোলাপী আভাখানি পুব আকাশে মৃদু সুরে আলাপ করছে।
ডঃ ভৌমিক তখনো ঘুমে। তাই তাঁর কাছে বিদায় নিতে পারলো না প্রত্যুষ। অনেক বেশী রাত অবধি কাজ করেন বলে এই প্রথম ভোরটুকুই তাঁর যা ঘুমের সময়।
স্টেলা হাসছিল। বলছিল, “বাব্বা, কত্তদিন পরে তোকে এমন হাসিখুশী দেখাচ্ছে। এতদিন ধরে তো কেবল দেখি হয় ল্যাবে ঠুক ঠুক করছিস, নয়তো গম্ভীরমুখে পড়াশোনা। দিন নেই রাত নেই, এই শুধু চলছে। ছেলের মুখে আর হাসি নেই। আজকে তোকে হাসতে দেখে আমারও ভালো লাগছে। মাঝে মাঝেই এইরকম ছুটি নিবি, বুঝলি? টিফিন বাক্সতে করে লুচি আর আলুর দম দিয়েছি। প্যাকেটে সন্দেশ আর কেক। মনে করে খাস কিন্তু সব।”
“আচ্ছা, আচ্ছা, খাবো। আমি তো তবু ছুটি নিয়ে পাহাড়ে যাই। তুমি তো একদিনও ছুটি নাও না। আমার জ্ঞান হয়ে থেকে তোমায় কোথাও যেতে দেখিনি।”
“ওমা, সংসার ফেলে যাবো কোথায়? তোকে আর বেশী পাকামো করতে হবে না। রওনা হয়ে পড়। রোদ উঠে গেলে কষ্ট হবে।”
প্রত্যুষ হেসে বেরোতে যাবার উদ্যোগ করতেই স্টেলা দৌড়ে এসে ওর কপালে একটা চুমো দিয়ে দৌড়ে আবার ঘরে চলে গেল। প্রত্যুষ শিহরিত।
পুব আকাশে টুকটুকে লাল সূর্যটা উঁকি দিয়েছে সবে। কোমল তার রূপ এখন। প্রত্যুষের বুকের ভিতরটা ছলছল করতে লাগলো।
গত রাতেই জুলিয়াকে ভুজুং ভাজাং দিয়ে কাটিয়েছে আজকের দেখা হওয়ার কথাটা। বলেছে, “জুলি ডার্লিং, বাবা নতুন একটা কাজের ভার চাপিয়েছেন। খুব ব্যস্ত থাকতে হবে। আজ দেখা হবে না জুলি। কিছু মনে কোরো না। বাবাকে তো জানোই। এবার আবার সময় খুব কম দিয়েছেন। এর মধ্যে কাজ না শেষ হলে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবেন।”
জুলিয়ার গলা শুনে বোঝা যাচ্ছিলো ও খুব হতাশ। কিন্তু ডঃ ভৌমিকের ইচ্ছার উপরে তো আর কোনো ইচ্ছা জয়ী হতে পারে না।
ওকে কাটিয়ে দিয়ে প্রত্যুষ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে শান্তির ঘুম। স্বপ্নে দেখেছে সেই প্রাণময়ী কিশোরীকে। সুকন্যা। অপরূপা সেই কিশোরী। বালিকার মতো তার মুখভাব, আশ্চর্য একটা পবিত্রতা লেগে থাকে ওর সর্ব অবয়বে।
স্বপ্নটা ভাবতে ভাবতে আবার গুঁড়ো গুঁড়ো আবীরে ভরে ওঠে প্রত্যুষের ফর্সা মুখ। এত নিবিড় আবেশে ভরা স্বপ্ন ছিল সেটা! যাঃ, এইরকম ঘনিষ্ঠ স্বপ্ন দেখা উচিৎ নয়। কিন্তু কী করবে ও? স্বপ্নের উপরে ওর কোনো কন্ট্রোল আছে নাকি?
পাহাড়ে উঠতে উঠতে ওর মন ফুরফুরে হয়ে যেতে থাকে। ভালোবাসায় আবার অনুচিত কী? ভালোবাসা আর যুদ্ধে সব চলে। যুদ্ধ? কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে প্রত্যুষ? নিজের বাবার সঙ্গে? ভাবতে ভাবতে আবার হাসলো প্রত্যুষ। স্বেচ্ছাচারী দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছে-এইরকম কাব্যিকভাবে ভাবতে কি দারুণ লাগে না?
কিন্তু ডঃ ভৌমিককে একেবারেই সাদাসিধে ভবভোলা দেখতে। মহিষাসুর, হিরণ্যকশিপু বা কংসের সঙ্গে একেবারেই কোনো মিল নেই। সত্যিই কি নেই? প্রত্যুষ জানে। সেই স্মৃতি ওকে তাড়া করে বেড়ায়। কতদিন আগের সেই সন্ধেবেলা এখনো কেন ওর মনের মধ্যে স্থির হয়ে আছে? উঃ, এর থেকে কি মুক্তি নেই?
চিবুকের কাটা দাগটায় চিড়িক করে উঠলো ওর। উঃ, এত ব্যথা কেন করছে আজকে? এরকম এত বেশী তো কোনোদিন হয় না?
“আঃ মাগো”, বলে হাত দিয়ে ওটা চেপে ধরে মাটিতে পড়ে গেল প্রত্যুষ। ভয়ানক মাথা ঘুরছে ওর। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।
অন্ধকারের মধ্যে ও দেখতে পেল একটা ছোট্টো ফুটফুটে ছেলেকে আর একটা ভয়ানক দৈত্যকে। ছেলেটার কচি কচি হাত দুটো দৈত্যের থাবার মধ্যে বন্দী। ছেলেটা ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে না। জানে, পারবে না।
দৈত্যটার মুখ কি কদাকার আর ভয়ানক! দৈত্য ছেলেটার হাত মুচড়ে দিল। বাচ্চা ছেলেটা ব্যথায় কেঁদে উঠতেই দৈত্য ওকে মারলো খুব জোরে। ছেলেটা পড়ে গেল মাটিতে। এরপর অট্টহাসি হাসতে হাসতে দৈত্য বিরাট বড়ো হয়ে যেতে লাগলো, আকাশে গিয়ে ঠেকলো দৈত্যের বিরাট মাথা। ও কি এখন বিরাট হাঁ করে ছেলেটাকে গিলে ফেলবে?
সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে দুঃস্বপ্ন ভেঙে উঠে পড়লো প্রত্যুষ। জামার বোতামগুলো খুলে খোলা হাওয়ায় গাছের ছায়ায় বসে রইলো খানিকক্ষণ। পিঠের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে জল খেল অনেকটা, চোখে মুখে জল দিল।
তারপরে একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে জামার বোতামগুলো আটকাতে আটকাতে ওর মনে পড়লো গতকাল বাবা ওর ল্যাবে মডেলটা দেখে প্রশংসা করে কতকিছু বলছিলেন সেই কথা। ছুটি চাইলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন হয়ে গেছিলেন। ও প্রশংসা শুনে হাসে না দেখে এমন বিচলিত হয়ে গেছিলেন! কেমন তাড়াতাড়ি করে ছুটি দিয়ে দিলেন! ভেবে হাসলো ও। ওর স্বপ্নে তিনি যে দৈত্য হয়ে যান, তা জানলে কি কষ্ট পাবেন উনি?
দূর, দূর, উনি এইসব পাত্তাই দেন না। এই তো প্রতুষ যে কোনোদিন বাবা বলে ডাকে না, উনি তো লক্ষ্যও করেন না।
শুধু স্টেলা আন্টি বলে উনি নাকি রাত্তিরে এসে ওর বিছানায় শিয়রের কাছে বসে থাকেন। প্রত্যুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন। ওর চুলে নাকি হাত বোলান। কই, প্রত্যুষ তো কিছু টের পায় না!
নিশ্চয় স্টেলা আন্টি বানায়। যাতে প্রত্যুষের মন ভালো হয়। একদিন স্টেলা আন্টি নাকি বাবাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে দেখে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন নাকি উনি খালি বলছিলেন, “স্টেলা, ও আমাকে বাবা বলে ডাকে না কেন? ও কি আমায় ঘেন্না করে?”
ধুস, এ-সব বানানো। কিন্তু আন্টিরই বা কি স্বার্থ? এমনিতে আন্টি কোনোদিন মিথ্যে কথা বলে না। শুধু শুধু তাহলে প্রত্যুষের কাছে কেন বানিয়ে বানিয়ে বলতে যাবে?
প্রত্যুষ অবশ্য সত্যিই বাবা ডাকে না ওঁকে। কেন ডাকবে? যাঁর কাছে গেলে কষ্ট হয় তাঁকে কেউ বুঝি বাবা ডাকে?
যদিও তিনি অনেক উপহার এনে দেন প্রত্যুষকে। সব পড়ে থাকে। কেন নেবে প্রত্যুষ? ওর ওসব ভালো লাগে না। আন্টি জানে। আন্টি দুঃখ পায়। প্রত্যুষ আন্টিকে বলেছে যেন বাবাকে না বলে দেয়। তাহলে হয়তো ভীষণ রেগে উনি দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে বসবেন। আন্টি বলে না। প্রত্যুষকে ভালোবাসে আন্টি। শুধু শুধু ও মার খাবে, এ চায় না হয়তো।
প্রত্যুষকে মারেন নাকি ওর বাবা? না, কোনোদিন মারেন নি তো আর! কিন্তু যদি কোনোদিন ধরতে পারেন তাহলে হয়তো খুব মারবেন। কী ধরতে পারবেন? এই যে প্রত্যুষ মানে না ওঁকে, নেয় না ওঁর দেওয়া উপহার, কথা না শুনে যে জায়গায় যেতে নেই সেখানে যায়!
প্রত্যুষ দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে কিচ্ছু বলবে না ও। যা খুশী করুক, প্রত্যুষ একটাও কথা বলবে না। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিচ্ছু বলবে না। ওকে মেরে ফেলুক, ভালোই হবে।
মরার আগে বলবে, “এই যে, ছোট্টো একটা বাচ্চা ছেলে যার মা নেই, তাকে ধরে বিনা কারণে যারা মারে, মেরে মুখ কেটে দেয়, পরেও কোনোদিন ক্ষমা চায় না, ভেবেছ তাদের কোনো অন্যায় হয় না? তারা আবার কিনা অন্যের অন্যায়ের সাজা দিতে আসে!”
ইশ, শুনে বুড়োর মুখ কেমন ভেবলুসের মতো হয়ে যাবে!
হাসির হাওয়া এসে ওর মনের মেঘ উড়িয়ে দিতে থাকে। আঃ, খুব মজা হবে তখন। দৌড়োতে দৌড়োতে ঢালু উপত্যকা বেয়ে নামতে থাকে ও। ঐ তো দেখা যায় গিরিপথের মুখটা। প্রায় অদৃশ্য দরজাটা খোলার কোড মনে মনে একবার আউড়ে নেয় ও।
“মিশিমাখা শিখিপাখা, এক তিন সাত পাঁচ নয়, চিচিং, নীল সাপ, বেদে, শিশিবোতল ছিপিঢাকা, আলোয় ঢাকা অন্ধকার, ঘন্টা, ঘন্টাকর্ণ, কস্তুরীগন্ধ” —কে দিয়েছিল এই সুন্দর কোডটা? নিশ্চয় সেই লোক লোক সুকুমার রায়ের লেখার ভারী ভক্ত ছিল। খুব ভালো স্মৃতিশক্তি না হলে কোনো না কোনোটা মিস হয়ে যাবেই। আর এটা উদ্ধার করাও ছিল এক চ্যালেঞ্জ। এত টাইট সিকিউরিটির ভিতর থেকে বার করে এনেছিল যে প্রত্যুষের নিজেকেই একটা কমপ্লিমেন্ট দিতে ইচ্ছে করছিল।
ডি-বাগিং মেশিনটা অন করে দরজা খুললো প্রত্যুষ। ভিতরে ঢুকে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ও এগিয়ে চললো গিরিপথটা ধরে, ঐ সূর্যমুখীর মাঠের দিকে। আহা, যদি থাকে ওখানে সুকন্যা!
এই ভোরে নরম আলো চারিদিকে! বসন্তের গাছেরা কী সবুজ, কী প্রাণময়! পাখিদের গানের মধ্যে যে এত সুর ভরা থাকে, তা কি এখানে না এলে কোনোদিন জানতে পারতো প্রত্যুষ?
ও গুনগুন করে কবিতা বলে— “ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির ঝরা ঘাসে / সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে / আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া ভাই / সর্ষে ফুলের পাপড়ি নেড়ে ডাকছে মোরে তাই।”
আঃ, কী নীল আকাশটা আজকে! তুলো তুলো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।
প্রত্যুষ এসে নদীর ধারের জলে ঝুঁকে থাকা পাথরটাতে বসলো। গাছের মিঠে ছায়া পড়েছে ওর উপরে। ব্যাগ থেকে ডাইরি আর পেন বার করে ও লিখতে শুরু করলো।
কী লিখছে? ওর এই নিষিদ্ধ ভ্রমণের কথা? না না, পাগল নাকি! কেউ পরে দেখে ফেললেই তো চিত্তির।
ও লিখছে গল্প। ফিকশন। অলকানন্দা বলে একটি মিষ্টি মেয়ে আর শীর্ষ বলে একটি ছটফটে কিশোরের মিষ্টি প্রেমের গল্প। তারই পরতে পরতে মিশিয়ে দিচ্ছে নিজের মন ও প্রাণের গোপণ কথা।
লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়ে দেখছে সূর্যমুখীর মাঠের দিকে। সুকন্যা আসবে না ওখানে? ও হয়তো এখন ওর কম্পুটিচারের কাছে পড়ছে।
লিখতে লিখতে মগ্ন হয়ে গেছিল, হঠাৎ দুটো নরম হাত পিছন থেকে ওর দু’চোখ চেপে ধরলো। ভয়ানক চমকে গেছিল প্রত্যুষ। তারপরে সুকন্যার খিলখিল হাসি শুনে ধাতস্থ হলো।
“ও তুমি! তা আজকে যে অন্যপথ দিয়ে? আগে তো ঐ মাঠের রাস্তাটা দিয়ে আসতে।”
“সবসময় এক রাস্তা দিয়ে আসতে কি ভালো লাগে নাকি কারুর? তোমাকে খুব চমকে দিয়েছি না?”
“হঠাৎ পিছন থেকে চোখ চেপে ধরলে চমকাবে না মানুষে? এ খেলাটা শিখলে কোথায়?
এখানে বুঝি সবাই এরকম করে?”
সুকন্যা হাসতে থাকে। বলে, “তবে যে বলো প্রত্যুষ ভয় পায় না?”
“এঃ, কে বললো ভয় পেয়েছি? চমকে গেছিলাম একটু, এই যা। ভয় কেন পাবো?”
“ইশ, তা বৈকি। ভয়ে বাবুর চোখমুখ সাদা হয়ে গেছিল যে একেবারে?”
“তাই নাকি? এমনিই আমার মুখ সাদা নয়? ভয় পেলে তবে সাদা হয়?” প্রত্যুষের মুখে দুষ্টুমীর হাসি।
সুকন্যা প্রত্যুষের হাত টেনে নিয়ে তার পাশে নিজের হাত রাখে। সুকন্যার হাল্কা বাদামী হাতের পাশে প্রত্যুষের হাত একেবারে ফুটফুটে ফর্সা, সাদাতে গোলাপীতে মেশানো এমনি সুন্দর রঙ যে সুকন্যা মুখ ভেঙিয়ে বলে, “আহা, ফর্সা বলে কী গর্ব! আমার মা যদি তোমার মায়ের মতন নরওয়ের মেয়ে হতো, তাহলে আমিও এরকমই হতুম।”
“কে বললো তোমায় আমার মা নরওয়ের মেয়ে ছিলেন?”
“আহা, বলবে আবার কে? ডেটাবেসেই তো সব আছে। কী সুন্দর দেখতে তোমার মাকে! আমি রোজ সকালে একবার ছবিটা দেখি।” সুকন্যা হাসছে।
“ও, আচ্ছা। তুমি আমার মায়ের ফ্যান হয়ে গেছ। তোমার মাকে কেমন দেখতে তা কিন্তু আমি জানিনা। এখানের কোনো খবর তো আর বাইরে যেতে পারেনা!”
“আমার মাকে দেখবে একদিন?”
“এই কী বলছো সুকু! জানোনা, এটা লুকোচুরি খেলা? ভুলে গেলে নাকি? কাউকে বলে দাওনি তো?”
“আচ্ছা, মায়ের ছবি এনে দেখাবো। কিন্তু তাহলে তুমি কী দেবে আমায়?”
“কী দেবো? দেবো একটা দারুণ মিষ্টি জিনিস।”
“কী জিনিস সেটা?”
প্রত্যুষের চোখে আবার সেই দুষ্টুমীর হাসি খেলে যায়। বলে, “এক্ষুণি চাই?”
প্রত্যুষ তার সুকুকে ঘন করে জড়িয়ে ধরে জীবনের প্রথম চুম্বনের নতুন মিঠে স্বাদ এঁকে দেয় ওর ঠোঁটে। শিহরিত ও আনন্দে অবশ-বিহ্বল ভাবে সুকন্যা তার মাথাটা এলিয়ে দেয় প্রত্যুষের বুকে।
বসন্তের বাতাস তার সমস্ত জাদু নিয়ে এই দুই কিশোর কিশোরীর ভালোবাসাবাসির চারিপাশে খেলা করে বেড়ায়। পাখির কিচির মিচির চির্প চির্প ওদের চারপাশে সুরতরঙ্গ তৈরী করে। নীল আকাশটা যেন উপুর হয়ে পড়েছে এই দুই বালক বালিকার লীলা দেখতে।
পক্ষী দম্পতি পরস্পরের চঞ্চুচুম্বন করতে করতে কথা কইছে। তা দেখে প্রত্যুষ আর সুকন্যা হাসছে। দূরে হরিণ হরিণীর গলায় গলা ঘষছে, দেখে ওরা হাসছে। প্রজাপতি বাতাসে নাচছে, মেয়ে প্রজাপতির মন ভোলাতে।
“প্রত্যুষ, জানো, প্রজাপতি এমনি করে ওড়ে মেয়ে প্রজাপতির মন জয় করতে। একে বলে কোর্টশিপ ডান্স। তুমি তো দেখি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ! তুমি তো কই নাচছো না?” সুকন্যা খুব হাসছে।
“প্রজাপতি তো ওড়ে, আমরা মানুষেরা উড়তে পারিনা দেখে একটা কাছাকাছি নাম দিয়েছি আরকি কোনোরকমে। কিন্তু সত্যি সত্যি নাচে কারা জানো?”
“ময়ূররা?”
“তোমাদের এখানে ময়ূর আছে? একদিনও তো দেখলাম না ময়ূর?”
“আছে ময়ূর। অনেক ময়ূর আছে। আর তুমি তো কালেভদ্রে দু’তিন ঘন্টার জন্য আসো।
তখন বাবুকে ময়ূরেরা এসে নাচ দেখিয়ে যাবেন। এঃ, কত শখ।”
“এই এই সুকন্যা, ময়ূরের নাচ দেখাতে পারবে একদিন? আমি ফোটো তুলে নিতাম। একেবারে ভিডিও ক্যামেরায়।”
“এসো বর্ষাকালে। বৃষ্টিতে ভিজে চুপ্পুস হয়ে দেখে যেও ময়ূরের নাচ। খুব মেঘ করে বিদ্যুৎ চমকালে, ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া বইলে তবে ওরা নাচে। তাও ময়ূরী সামনে থাকতে হবে।”
“বনময়ূরী, তুমি সামনে থাকলেই ওরা নাচবে।” বলেই প্রত্যুষ আবার ওকে জাপ্টে ধরে। একবার খেয়ে ওর নিজেরই তেষ্টা বেড়ে গেছে।
“এই কী হচ্ছে? শিগগির ছেড়ে দাও। বাড়াবাড়ি কোরো না বলছি।”
“কেন, কে আছে এখানে যে দেখবে?”
সুকন্যা সুকৌশলে প্রত্যুষের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে চলে যায়। বলে, “প্রত্যুষ, তুমি তো জুলিয়াকে অনেক চুমু খেতে পারো। তাহলে এইরকম খাই খাই করছো কেন?”
“আরে আরে, কান্ড দেখো! এসব কথা তুমি শিখলে কী করে? আর জুলিয়াকে আমি চুমো খাই কে বললো? ও ই বরং জোর করে আমাকে খায়।”
“আরো কতগুলো বান্ধবী আছে তোমার প্রত্যুষ? অনেক?”
প্রত্যুষ দু’হাত দু’পাশে ছড়িয়ে দেয়। বলে, “অনেক, অনেক, অনেক। একজন তো আমার ঘরে আমার সঙ্গেই থাকে। তার আবার অনেক বয়ফ্রেন্ড। সকাল হলেই জানালা দিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যায়, সেইসব বয়ফ্রেন্ডদের কাছে। সন্ধে হলে তবে এই বেচারাকে ওর মনে পড়ে। তখন ফিরে আসে আবার সেই জানালা দিয়েই। ওর জন্য বিস্কুট টুকরো করে রাখি। ও থাকে অনেক উঁচুতে তাকের উপরে। একটা মেয়ে চড়াই, ওর নাম দিয়েছি চুলবুলি।”
সুকন্যার মুখ আলো হয়ে যায়। বলে, “আর আর অন্য আরো বাকীরা?”
“আরেকজন আছে খুব দূরে। কক্ষোণো কাছে আসে না। এখন সন্ধে হলেই তাকে দেখতে যাই প্রত্যেকদিন। সে তার বয়ফ্রেন্ডের গলা জড়িয়ে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে। শরতে শীতে তাকে আর সন্ধেয় দেখা যায় না। তখন সে শেষ রাতে ওঠে। কে বলো তো?”
আবিষ্ট চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে সুকন্যা বলে, “আমি জানি। সে অরুন্ধতী তারা।” তারপরেই মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠে বলে,” বশিষ্ঠ ঋষি জানতে পারলে তোমাকে কী করবেন জানো?”
প্রত্যুষ হেসে বলে, “বশিষ্ঠ ঋষি খুব ভালো। তিনি বরং আমাকে খুব কমপ্লিমেন্ট দেবেন। বলবেন, সাবাস, এই তো চাই।”
সুকন্যা বলে, “তাই বলবেন? এঃ, তুমি খুব জানো। রেগে রক্তচক্ষু হয়ে বলবেন, রে দুষ্ট বালক, আমার বৌয়ের দিকে নজর দেওয়া? আয় তোরে এখনি ব্রহ্মশাপে করে দিই ভস্ম।” বলে হেসে লুটিয়ে পড়ে।
“আরে, আরে তুমি নাটকও করো নাকি? এরকম গলা পাল্টাও কিকরে?”
“এই এই কথা ঘুরিয়ে পালানোর চেষ্টা কোরো না। মোটে দু’জনের নাম বলেছ। তোমার বাকী বান্ধবীরা?”
কৃত্রিম কাতর ভঙ্গী করে প্রত্যুষ বলে, “অনেক যে! বলতে গেলে দিন কাবার হয়ে রাত ঘনিয়ে আসবে। তার চেয়ে এসো না, আমরা ঐ বনের দিকটায় গিয়ে ময়ূর খুঁজি?”
বনের মধ্যে ময়ূর খুঁজতে খুঁজতে এই দুই কিশোর কিশোরীর খুনসুটির হাল্কা শব্দে নির্জনতাপ্রিয় পাখিরা ডানা ঝটপট করে উড়ে যায়।
“ইশ, এত আওয়াজ হলে ময়ূর কেন, বাঘ অবধি পালিয়ে যাবে।”
প্রত্যুষের হাতে ক্যামেরা, ময়ূর দেখলেই ছবি তুলবে বলে রেডি হয়ে আছে।
তারপর থেকে অনেক বার এভাবে ঢুকেছে প্রত্যুষ, অনেক অনেক ভালোবেসেছে তাঁর সুকুকে। কেউ কিচ্ছুটি জানতে পারেনি।
চার বছর ধরে এমনি লুকোচুরি খেলায় ওদের একটুও ক্লান্তি আসে নি। কিন্তু একদিন ষোলো বছরের সদ্য ফোটা যুবতী সুকন্যা প্রত্যুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে চাইলো।
প্রত্যুষ এর বিপদের দিকটা জানতো, সে প্রথমে বেশ কদিন নানা কথায় এড়িয়ে গেলো। সে চাইছিলো না যে সুকন্যা জানুক কি প্রচন্ড বন্দীত্বের মধ্যে সে আছে।
কিন্তু একদিন সুকন্যা তাঁকে ঠাট্টা শুরু করলো, বললো, “তবে যে বলো, তুমি কাউকে ভয় করো না!”
আরো অনেক কথা বলে ওকে তাতিয়ে দিলো সুকন্যা। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল প্রত্যুষের।
সেই সূর্যমুখীর মাঠে দু’জনে মিলিত হবার পর কেমন যেন অবসন্ন মন নিয়ে ফিরে গেল প্রত্যুষ। আকাশের দিকে চেয়ে শান্ত হয়ে পড়ে ছিল মিলনতৃপ্ত সুকন্যা-এত অবিষ্ট যে প্রত্যুষকে বিদায় অবধি জানাতে পারেনি ভালো করে।
তিনমাস পরে মেডিকেল চেকিং এর সময় ধরা পড়ে গেল সুকন্যা।
(৫)
সীবলী শুনে হতভম্ব হয়ে গেল প্রথমে। সুকন্যা অন্তঃসত্ত্বা! তার চেয়েও আরো ভয়ংকর ব্যাপার হলো তার গর্ভস্থ সন্তানের জেনেটিক প্রোফাইলের সঙ্গে এই Ecosphere 2 এর কারুর জেনেটিক প্রোফাইলের মিল নেই! তার অর্থ অতি ভয়ংকর। এই সন্তানের বাবা বাইরের পৃথিবীর মানুষ, যা এই প্রোজেক্টের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ংকর পাপ, তা করে বসেছে সুকন্যা!
সীবলীর মথায় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা শুরু হয়, সে কপাল টিপে ধরে বসে পড়ে। এই সুন্দর সরল পবিত্র মুখের কন্যা, তার সামনে বসে আছে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে, সে তো জানেও না কী চরম শাস্তি অপেক্ষা করছে তার জন্যে ও তার অনাগত সন্তানের জন্যে।
সীবলী ভালো করে ভাবতে পারে না, ডঃ ভৌমিক, যিনি সামান্যতম ভুল ও সহজে বরদাস্ত করেন না, তিনি এটা জানার পর চরম পথ ছাড়া আর অন্য কোনো পথের কথা কি ভাববেন? এই সুকন্যা, আদিত্য, শতদ্রু —এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কি তাঁর কাছে গিনিপিগের চেয়ে বেশী কিছু? আর তারা, দ্বিতীয় জীবমন্ডলের স্বেচ্ছসেবকেরা? তারাও তো স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস হয়েছে, কিছুই কি বলতে পারবে এর বিরুদ্ধে? বললেও কি শুনবে সেই নিরাসক্ত গবেষক বাহিনি?
সীবলী সুকন্যার দু’হাত শক্ত করে চেপে ধরে রাগি চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের ভিতরটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সীবলীর। কী করবে সে? নিজেই শাস্তি দেবে ওকে? সীবলীর নিজেরও কি প্রোজেক্ট নয় এটা? সেই পরীক্ষা কন্টামিনেট করে দিয়েছে এই মেয়েটা।
সুকন্যার চোখে একটুও ভয় নেই, সংকোচ বা লজ্জাও নয়। আবিষ্ট ওর দুটি চোখ,সর্ব অবয়বে কোমলতা ফুটে আছে। কী যেন অনুভব করেছে সে, কোন্ অজানা অমৃতের স্বাদ, তাই বাকী সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। তাই সীবলীর হাতে প্রচন্ড মার খাবার সময় একেবারে চুপচাপ থাকে সুকন্যা। দরজা বন্ধ ঘরে পাগলের মতন হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতন মারছিলো সীবলী, ভুলে গেছিলো যে এ তার বড়ো আদরের একমাত্র সন্তান। সুকন্যার গালে সীবলীর পাঁচ আঙুলের চাপ পড়ে গেল,ও কিছু বুঝতেই পারলো না। ওর জামা ছিঁড়ে গেল, কঞ্চির আঘাতে পিঠে লম্বা লম্বা দাগ পড়ে গেল, কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেলো–ও কিছু ব্যথা বুঝতেই পারছিলো না। ওর মন জুড়ে ছিলো শুধু সেই নদীর তীর, সূর্যমুখীর মাঠ,সেই নীলার মতো নীল আকাশ। আর সেই হাসিমুখের প্রত্যুষ।
কী সে দিয়ে গেছে সেও কি জানে? সুকন্যার জীবনপাত্র ভরে কি অনাস্বাদিত সুধা? মুক্তির স্বাদ! ঐ তারাস্পর্শী অনুভূতি কি কখনো হারায়? ওরই জন্য পৃথিবীর সব বেদনা অমৃত হয়ে গেছে যে!
মারধর শেষ করে সীবলী নিজেই ভেঙে পড়লো কান্নায়, দু’হাতে সুকন্যার মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে অঝোরে কাঁদছিলো সীবলী। ওর অশ্রু ভিজিয়ে দিচ্ছিলো বক্ষলগ্না সুকন্যার চুল।
সুকন্যা মুখ তুলে মাকে দেখলো। ওর কোনো রাগ বা দুঃখ ছিলো না। কোনো অভিমান পর্যন্ত নয়। অনায়াসে হাত বাড়িয়ে সে মুছে দিতে লাগলো সীবলীর গালের উপর থেকে অশ্রুর ফোঁটাগুলো। বালিকার মতন গলায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কেন কাঁদছো তুমি?”
শুনে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না সীবলী। সুকন্যাকে পাগলের মতন চুমো খেতে খেতে বললো, “পালিয়ে যাবো, তোকে নিয়ে পালিয়ে যাবো বাইরে। কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তোর।” বলেই চমকে ওঠে সীবলী, কেন সে বললো? এ তো চলে গেল ওদের রেকর্ডে! আহ, কেন সে নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না?
সেই একই রকম অবাক গলায় সুকন্যা বললো, “ক্ষতি? কে ক্ষতি করবে আমার? কেন করবে?”
হাহাকারের মতন সীবলী বললো, “ওরে তুই জানিস না কী করছিস তুই। এ যে ভয়ানক পাপ! এই প্রোজেক্ট কন্টামিনেট করে দিয়েছিস। তোকে— ওহ, তোকে ওরা–”
ভয়ে গলা আটকে যায় সীবলীর। সুকন্যা হাসে, আলতো করে ছোঁয় সীবলীর কপাল, গাল, গলা। আস্তে আস্তে বলে, “ভয় কোরো না মা। কেউ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।” সীবলী থমকে চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে। সুকন্যা কিছু লুকোচ্ছে আরো? কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস ও তো করা যাবে না, সবকিছু যে বাইরের ওদের নজরদারিতে!
ওদিকে প্রত্যুষও ধরা পড়ে গেছিলো। সুকন্যা ধরা পড়েছে জেনে সে নিজেই এসে কবুল করেছিলো যে Eco2 তে সে অনেক দিন ধরে যাচ্ছে, প্রায় চার বছর ধরে সুকন্যার সঙ্গে মিশছে, সব দোষ প্রত্যুষের, সুকন্যার কোনো দোষ নেই।
দিশেহারা বিজ্ঞানীরা ওকে আটকে রাখেন ডঃ ভৌমিকের প্রাসাদের একটি জানালাহীন ঘরে। সম্পূর্ন আসবাবহীন অদ্ভুৎ ঘরটা, শুধু অনেক উপরে একটা ছোট্টো ঘুলঘুলি দিয়ে খুব অল্প আলো আসছিলো। সেই আলোতে শুধু দেখা যায় দেওয়ালে আটকানো একটা আয়না।
আয়নার সামনে গিয়ে প্রত্যুষ নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করে, অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছে না ভালো, কিন্তু তাও ওর চিবুকের পুরানো অথচ স্পষ্ট ক্ষতচিহ্নটা দেখতে পায়, তিক্ত একটা হাসি ফোটে ওর ঠোঁটে।
মোটা ইস্পাতের দরোজা শক্ত করে বন্ধ করা ছিলো। স্টেলা কিচ্ছু জানতে পারেনি, জানলে হয়তো ডঃ ভৌমিকের কাছে ওকে বাঁচাবার আবেদন করতো।
বিজ্ঞানীরা ঘোর সমস্যায়। কী করা হবে ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে। সুকন্যা ওদের এক্সপেরিমেন্টের অঙ্গ, ওকে যতো সহজে এলিমিনেট করে দেওয়া হবে, প্রত্যুষকে শাস্তি দেওয়া তত সোজা নয়।
প্রত্যুষ সাবালক ও বাইরের পৃথিবীর নাগরিক। ওকে মেরে ফেলা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব নয়, খুনের দায়ে পড়ে যাবেন তাহলে তাঁরা। বড়ো জোর ওকে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে ফেলা যায়, কিন্তু তাও কতটা সম্ভব কেউ বলতে পারছেন না। ও নিষেধ না মেনে Eco2 তে ঢুকেছিলো এটা এই বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের কাছে অপরাধ, বাইরের পৃথিবীর তো তাতে কোনো মাথাব্যথা নেই!
কিন্তু সুকন্যাকে যে এলিমিনেট করে ফেলা হবে, সেটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠছেন সবাই, এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। সবার মনে পড়ছে সুকন্যার নিস্পাপ সরল মুখ, উজ্জ্বল কৌতূহলী চোখ, আশ্চর্য হাসি। ডঃ ভৌমিক নিজের চুল মুঠো করে ধরে টেবিলে মাথা নামিয়ে বসে আছেন, কী বলবেন তিনি? সবাই অপেক্ষা করছে, শুধু তিনি ঘাড় হেলিয়ে “হ্যাঁ” বলামাত্র সুকন্যাকে বার করে এনে ঢুকিয়ে দেবে সেই কুঠুরিতে, যেখানে কারবন-মনোক্সাইড গ্যাসে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুঘুম নেমে আসবে ওর চোখে।
এইমাত্র খবর এলো ভিতরে সীবলী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন, সুতণু নিজের দুঃখ বুকে চেপে যথাসাধ্য ওষুধপত্র দিচ্ছেন এখানকার নির্দেশ অনুযায়ী।
(৬)
সুকন্যা কিন্তু একটুও কিচ্ছু খারাপ বা ভয়ের কথা ভাবছিলো না, কেবল ভাবছিলো নদীর ধারটা আর সেই সুন্দর লেবুগন্ধী ঘাসগুলোর কথা। একসময় সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো একা। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়া মাকে নিয়ে পাশের ঘরে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত।
ডি-বাগিং মেশিন অন করে ও বাড়ী ছেড়ে সোজা সেই নদীতীরে। হাতের আঙুলে পরা যোগাযোগ যন্ত্রটা চালিয়ে বললো, “প্রত্যুষ, শুনতে পাচ্ছ?”
বন্ধ ঘরের ভিতরে প্রত্যুষের গলার চেনে আটকানো রিসিভারে সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। জামার ভিতর থেকে ওটা বার করে এনে ও ব্যাকুল গলায় বললো, “সুকু! কেমন আছো তুমি? তোমাকে ওরা কিছু–আহ, আমি একটা বুদ্ধু, নিজের অহংকারে তোমায় বিপদে ফেললাম। তোমায় আগেই বলেছিলাম, কেন তুমি জোর করলে—” কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রত্যুষ।
সুকন্যা কিন্তু একটুও ভাঙে না, ঘাবড়ায় না, দুর্বল হয় না। সে দৃঢ় গলায় বলে, “ছি ছি, তুমি ভেঙে পড়ছো? আমাদের কী কথা ছিলো? ওদের ভয় পাবো, তাই কথা ছিলো নাকি? তুমিই না বলেছিলে, আমরা দু’জনে এমন জায়গায় পালাবো যে ওদের কারুর সাধ্য নেই ধরে?”
কোনো রকমে সামলে নিয়ে প্রত্যুষ বলে, “তুমি কোথায় সুকু? কোথা থেকে কথা বলছো? তোমার ডিবাগিং অন আছে নাকি নেই?”
হাসে সুকন্যা, বলে, “আছে। এত বোকা নাকি তোমার সুকু? আমি বাড়ী থেকে নদীতীরে চলে এসেছি। এবারে এখানে থেকে চলে যাবো। এই আবদ্ধ ও সংকীর্ন মানুষের মধ্যে কক্ষণো আমার মৈত্রেয় আসবে না। সে আসবে অনেক মুক্ত ও ভালোবাসায় ভরা জগতে।
এ আমি একেবারে প্রথম থেকে জানি।”
এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেলে প্রত্যুষ, “বাঃ, দারুণ নাম ঠিক করেছ তো! মৈত্রেয়। দারুণ। জানলে কি করে মৈত্রেয়ী নয়?” আবার হাসে সুকন্যা, বলে “সত্যি তুমি না একটা কি যেন। এত আল্ট্রা সব যন্ত্রপাতি তাহলে কি করতে?”
তারপরে কোমল গলায় বলে, “একসঙ্গে যেতে পারলে ভালো হতো প্রত্যুষ। কিন্তু গিয়ে তো দেখা হবেই, তাই না? অনেক আদর নাও। এবারে রাখি?”
প্রত্যুষ আঁধার ঘরে যোগাযোগ যন্ত্রটার উপরে চুমো খেতে খেতে রুদ্ধ গলায় বলে, “সাবধানে যেও। আমি আসছি। তোমাকেও অনেক আদর।” যন্ত্র বন্ধ করে আয়নাটার দিকে এগিয়ে যায় ও।
নদীতীরের জঙ্গল থেকে সুকন্যা তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিড়ে নিলো ধারালো ঘাসের ফলা। তারপরে দু’হাতের কব্জি চিরে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লো নদীর উপরে ঝুঁকে থাকা চ্যাটালো পাথরখানায়। ওর দু’হাত বেয়ে তাজা রক্তধারা বয়ে যাচ্ছিলো, খুব আনন্দ হচ্ছিলো সুকন্যার, খু ব শান্তি এবারে। কত কতদিন সে বন্দী ছিলো এই সোনার খাঁচায়!
আলতো ঘুমঘুম গলায় সে কবিতা বলছিলো, “খাঁচার পাখি ছিলো সোনার খাঁচাটিতে /বনের পাখি ছিলো বনে / একদা কেমনে জানি মিলন হ’লো দোঁহে/ কী ছিলো বিধাতার মনে।” ঘুরে ফিরে এই লাইন কটা বলে যাচ্ছিলো। আহ, শীত করছে কেন ওর এত?
তলপেটে হাত রাখলো সে, তিরতিরে কম্পন সেখানে? ও কি বুঝতে পারছে? বুঝতে পারছে যে মায়ের সঙ্গে সেও পাড়ি দিচ্ছে অজানা উজান?
ফিসফিস করে সুকন্যা বললো, “আর দেরি নেই। আর দেরি নেই বেশী। আর একটুখানি। তারপরেই আমরা অন্যখানে। কেমন মজা? হি হি হি। কেউ খুঁজে পাবে না আর।”
এদিকে সেই বন্ধ ঘরের ভিতর প্রত্যুষের সজোর ঘুষিতে ঝনঝন করে ভেঙে গেল আয়নার কাঁচ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচের টুকরো। ভালো ভালো দেখে তেকোনা তেকোনা হয়ে ভাঙা কাঁচ তুলে নিলো প্রত্যুষ। তারপরে সেও নিজের দুখানা কব্জি ঘষে চিরে দিলো। লাল নদী বয়ে যেতে লাগলো মেঝে ভাসিয়ে, লোহার দরজার তলা দিয়ে রক্তধারা বাইরে আলোয় বেরিয়ে আসতে লাগলো। আঁধার ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে প্রত্যুষ তাকিয়ে ছিলো ঐ উপরে ঘুলঘুলিটার দিকে। সেখান দিয়ে আসা অল্প আলোয় সে দেখতে চেষ্টা করছিলো আকাশ। অনেক বড়ো আর আলোয় ভরা আকাশ।
চেতনা হারাবার আগে ও মনে মনে শুনতে পেলো সুকন্যার খিলখিল হাসি আর কথা। “কই, প্রত্যুষ,তুমি যে দেখি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ? তুমি তো কই নাচছো না?” আবার শুনতে পেলো আলো-আলো মুখে সুকন্যা বলছে “জানি, সে অরুন্ধতী তারা। বশিষ্ঠ ঋষি শুনতে পেলে তোমায় কি বলবেন জানো?” অস্ফুটে প্রত্যুষ বললো, “আমি আসছি সুকু, আসছি।”
আহ, এত শীত করছে কেন ওর?
প্রত্যুষের ঘরের দরজা খুলেছিলো রোহিত, ঐ Eco2 প্রকল্পের সিকিউরিটি অফিসার। একবার দেখেই বুঝতে পেরেছিলো যে প্রত্যুষ নেই আর। চিৎকার করে উঠেছিলো রোহিত। তারপরেই নিজে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলো মেঝেতে।
সুকন্যাকে নদীতীরে দেখতে পেয়েছিলো জাগর১ বলে Eco2 এর একজন সিকিউরিটি রোবট।
দু’জনের সমাধি একই জায়গায়, ওহ, দু’জন নয়, তিনজন। ওদের অজাত সন্তানটিও তো! বাবা, মা আর তাদের জন্ম না নেওয়া সন্তানের দেহাবশেষ শুয়ে আছে সবুজ ঘাস আর ফুলে ঢাকা প্রান্তরে।
ডঃ ভৌমিক নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে চলে গেছেন অজ্ঞাত স্থানে, সঙ্গে হাজার বারণ সত্বেও গেছে স্টেলা। মানসিক ভারসাম্য হারনো সীবলীর শুশ্রুষা করে চলেছে সুতনু। বাকী সব দায়দায়িত্ব থেকে ওদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, যথাসাধ্য করছেন ডাক্তারেরা। সবাই আশা করছে একদিন হয়তো আবার স্বাভাবিক মন ফিরে পাবে সীবলী।
সমস্ত নদীরা একই ভাবে বয়ে চলেছে, বাইরে আর ভিতরে। সোনার পাহাড়ে একই ভাবে ঝলমল করে সর্বদর্শী সূর্যের অমল কিরণ। ভিতরের আর বাইরের বনে বনে একইভাবে পাখপাখালি গাছগাছালির চক্রাবর্তন, সুখে ও দুঃখে, আনন্দ ও বিষাদে।
সেই ঝুঁকে পড়া চ্যাটালো পাথরটার ধারে ধারে লতাগুলো ফুলে ফুলে ভরে ওঠে প্রতি বসন্তে, গ্রীষ্মে ফল ধরে, শীতে আবার সব ফল পাতা ঝরে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। পাখিরা পাখা ঝাপটিয়ে খুনসুটি করে।
সব একইরকম আছে, শুধু সেই সাহসী ছেলেমেয়ে দু’টি আর কোত্থাও নেই।
Tags: অধরা বসুমল্লিক, কল্পবিজ্ঞান গল্প, কৌশিক সিনহা চৌধুরী, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
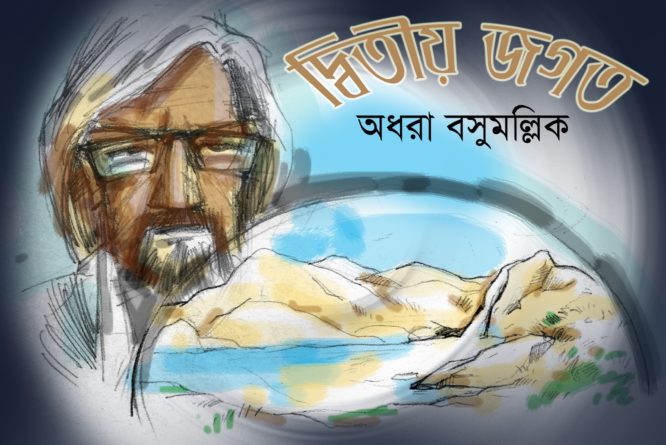

very very nice